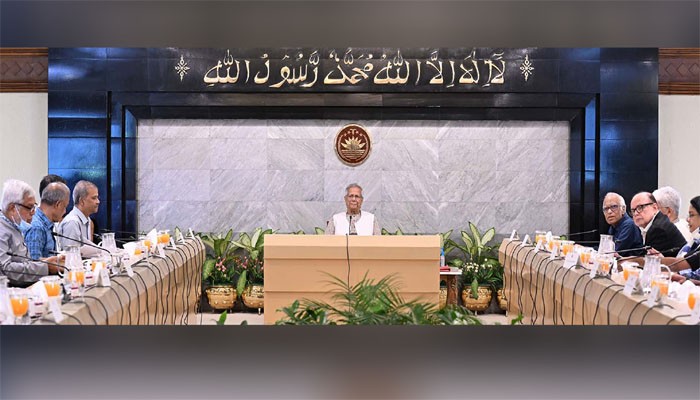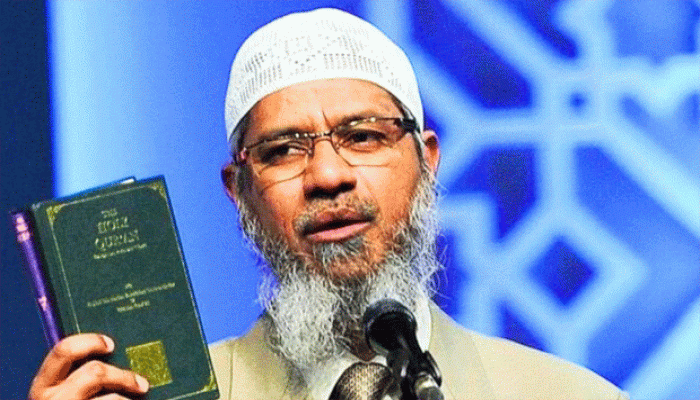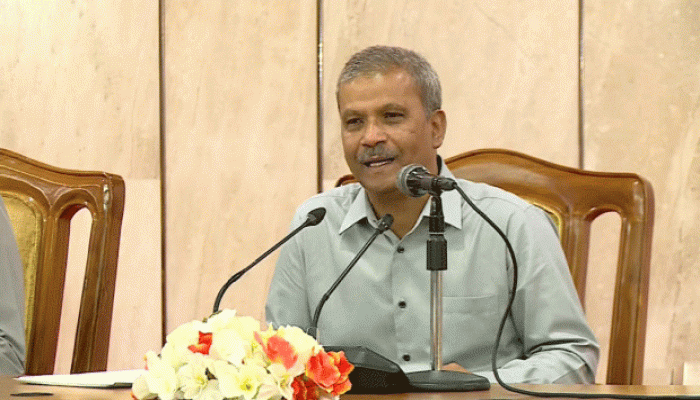চলতি বছরের মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিভিন্ন শর্ত মেনে চলছে সরকার। সংস্থাটির পরিমাণগত কর্মক্ষমতা মানদণ্ড অনুযায়ী, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চলতি বছরের জুনে ২৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৫ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার এবং ডিসেম্বরে ২৬ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারের নিচে থাকতে পারবে না। অথচ বর্তমানে রিজার্ভ রয়েছে ২১ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা বেশি। চলতি সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে (বিপিএম৬) রিজার্ভ ছিল ২৩ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ডলার। ২০ সেপ্টেম্বর তা ২১ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। অর্থাৎ চলতি সেপ্টেম্বরের প্রথম ২০ দিনেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার ক্ষয় হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২১ সেপ্টেম্বর এ তথ্য জানানো হয়।
বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২২-২৩ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে রেকর্ড সাড়ে ১৩ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছে। আর চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২১ সালের আগস্টে দেশের গ্রস রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। তার পর থেকেই রিজার্ভের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে কমছে।
রিজার্ভ বৃদ্ধির প্রধান উৎস হলো প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত রেমিট্যান্স-প্রবাহ বেশ মন্থর। সর্বশেষ গত আগস্ট মাসে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের প্রবাহ ২১ দশমিক ৪৮ শতাংশ পতন হয়েছে। চলতি মাসের প্রথম ১৫ দিনে এসেছে কেবল ৭৩ কোটি ডলার। রেমিট্যান্স আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়ার কারণেই দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় প্রতিদিনই রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে; তাও আবার জ্বালানি তেল, এলএনজি, সারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির দায় মেটানোর জন্য। পাশাপাশি সরকারের বিদেশি ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্যও ডলার বিক্রি করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে।
রেমিট্যান্সে বড় ধরনের পতন হওয়ায় রিজার্ভের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। তারা বলছেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) জুলাই-আগস্ট মেয়াদের আমদানি দায় বাবদ ১৩১ কোটি ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে। আবার রিজার্ভ থেকে বাজারে ডলার বিক্রিও অব্যাহত রাখা হয়েছে। এসব কারণে সেপ্টেম্বরে রিজার্ভের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে কমে যাচ্ছে। মাস শেষে রিজার্ভ ক্ষয়ের পরিমাণ ২ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকতে পারে বলে সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা।
দেশে রেকর্ড হারে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমার পর জ্বালানি সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। আমদানি-নির্ভর জ্বালানি খাত হওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহে হিমশিম খাচ্ছে সরকার। পর্যাপ্ত ডলার মজুত না থাকায় এলএনজির বড় চালানও আমদানি করা যাচ্ছে না। কয়লা সংকটে ধুঁকছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো। বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ধারাবাহিকভাবে কমলেও নিয়মিত জ্বালানি আমদানি করতে হচ্ছে। সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত।
অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, জ্বালানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্যাসের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। এই অবস্থায় আমদানি করার বিকল্প নেই। আমদানির সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প উপায়গুলো নিয়েও ভাবতে হবে বলে মনে করছেন তারা। তবে জ্বালানি বিশ্লেষকেরা বলছেন, চড়া দামের এলএনজি আমদানির কারণে সার্বিকভাবে উচ্চমূল্যের গ্যাসের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের অর্থনীতিতে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে তীব্রভাবে পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশ।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে কারণে সংকট দেখা দিয়েছে, এখন তার উল্টো কাজ করতে হবে। স্বল্প অথবা দীর্ঘমেয়াদে গ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্যাস উত্তোলন বাড়াতে পারলে সংকট অনেকটা কেটে আসবে। মূল সমস্যা জ্বালানি। জ্বালানি কিনতে গিয়ে অন্য অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তারা আরও বলেন, দেশীয় উৎস থেকে তেল-গ্যাস আহরণের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তা না করে আমদানি-নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। ডলার সংকট হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কলকারখানা চালু রাখতে হলে জ্বালানি আমদানি করতে হবে। এর বিকল্প নেই। সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব হওয়ায় এলএনজি আমদানি করা উচিত। যত দ্রুত সম্ভব দেশীয় উৎস থেকে তেল-গ্যাস আহরণের দিকে জোর দিতে হবে।
এদিকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পূর্বাভাসকে স্থিতিশীল থেকে নেতিবাচকে নামিয়ে এনেছে আন্তর্জাতিক ঋণমান সংস্থা ফিচ রেটিংস। তবে ঋণমানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বা লং টার্ম ফরেন কারেন্সি ইস্যুয়ার ডিফল্ট রেটিং (আইডিআর) ‘বিবি মাইনাসে’ বহাল রেখেছে সংস্থাটি। অর্থনৈতিক পূর্বাভাস স্থিতিশীল থেকে নেতিবাচকে আনার বড় কারণ হিসেবে ফিচের প্রকাশিত প্রতিবেদনে রিজার্ভের পতন ও ডলার সংকটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের নেওয়া নীতিগত পদক্ষেপ এবং বিদেশি আনুষ্ঠানিক ঋণদাতাদের ক্রমাগত সহায়তাও রিজার্ভের পতন ও স্থানীয় বাজারে ডলার সংকট প্রশমন করতে পারেনি।
দেশের অর্থনীতির সংকট এখন বহুমাত্রিক বলে মনে করেন সাবেক গভর্নর ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, অর্থনীতির খারাপ পরিস্থিতির জন্য এখন শুধু কোভিড ও ইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করার সময় আর নেই। বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যের চেয়েও অভ্যন্তরীণ সংকটের মাত্রা অনেক বেশি। দেশের ব্যাংকসহ আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। মুডি’স-এসঅ্যান্ডপির মতো ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠানগুলো একযোগে দেশের ঋণমানকে নেতিবাচক করে দিচ্ছে। এগুলো অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে বিপর্যয় ডেকে আনবে।
এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বদরুল ইমাম বলেন, সরকার বিরাট আকারে এলএনজি আমদানির যে পরিকল্পনা করেছে, তা অর্থনীতিতে একটি বড় প্রভাব পড়বে। এলএনজির বিকল্প বাংলাদেশের সামনেই ছিল। ২০১২ সালে মিয়ানমারের কাছ থেকে আমরা যে সমুদ্রসীমা জয় করেছি, অনুসন্ধান চালালে সেখানে নিয়মিত গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মিয়ানমার আমাদের বর্ডারের কাছেই গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। এ ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থায় স্বল্পমেয়াদে অল্প পরিমাণ আমদানি করা যেতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
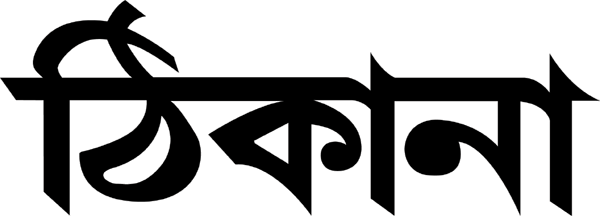
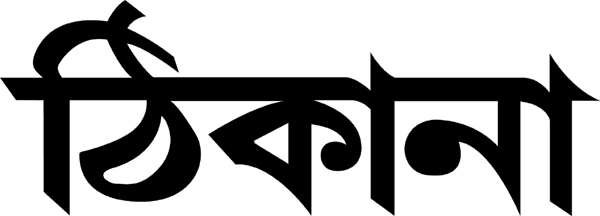



 ঠিকানা রিপোর্ট
ঠিকানা রিপোর্ট