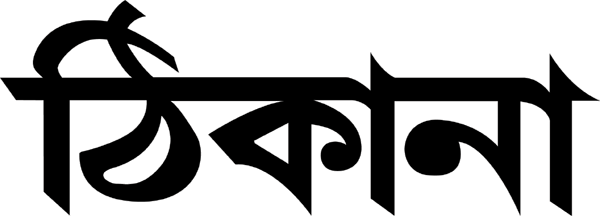মনজুর আহমদ : নিউইয়র্কে কোন বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটি সর্বাধিক প্রচারিত? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব কি কারও কাছ থেকে পাওয়া যাবে? আসলেই এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ, পত্রিকার প্রচারসংখ্যা হিসাব করার কোনো সহজ পন্থা এখন নেই। নিজের পত্রিকাকে ‘সর্বাধিক প্রচারিত’ বলে জাহির করার একটা প্রবণতায় আমরা কম-বেশি সবাই আক্রান্ত। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা সবাই নিজেদের পত্রিকাকে সর্বাধিক প্রচারিত বলে দাবি করে থাকি। কেন প্রচারসংখ্যা বেশি দাবি করা নিয়ে আমাদের মধ্যে এমন একটি অযৌক্তিক প্রতিযোগিতা? কারণ, প্রচারসংখ্যা একটি পত্রিকার জনপ্রিয়তার প্রধান মাপকাঠি। প্রচারসংখ্যা বেশি হওয়াটা যেকোনো পত্রিকার জন্যই গর্বের বিষয়। নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রভৃতি পত্রিকার সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে আমরা সেগুলোর বিপুল প্রচারসংখ্যার কথা উল্লেখ করি। বাংলাদেশেও তো মানুষ প্রচারসংখ্যার ভিত্তিতেই সেখানকার পত্রিকাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সেখানকার প্রচলিত ব্যবস্থায় কারও জানতে অসুবিধা হয় না কোন পত্রিকার প্রচারসংখ্যা কেমন। সেই পঞ্চাশের দশকে ছিল দৈনিক আজাদ। অনেক দিন পর্যন্ত ঢাকায় আর কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকা না থাকায় আজাদের ছিল একচেটিয়া সার্কুলেশন। পরবর্তী সময়ে দৈনিক ইত্তেফাক সর্বোচ্চ প্রচারসংখ্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আরও পরে দৈনিক বাংলা, নব্বইয়ের দশকে জনকণ্ঠ এবং এখন প্রথম আলো ঘরে ঘরে সমাদৃত।
কীভাবে নির্ধারিত হয় পত্রিকার প্রচারসংখ্যা? স্পষ্টতই বলা যায় পত্রিকার বিক্রির হিসাবে। কোন পত্রিকা কত বিক্রি হলো, সেটাই তার সার্কুলেশনের ভিত্তি। হ্যাঁ, বিক্রি। এ কথা তো অনস্বীকার্য, পত্রিকা বিক্রি দিয়েই প্রমাণিত হয় তার প্রচারসংখ্যা এবং প্রচারসংখ্যা দিয়েই বিবেচিত হয় তার জনপ্রিয়তা। যে পত্রিকার যত সার্কুলেশন, সেই পত্রিকাই যে তত জনপ্রিয়, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকার অবকাশ নিশ্চয় নেই। জনপ্রিয়তার যাচাই করেই মানুষ পকেটের পয়সা দিয়ে তার পছন্দের পত্রিকাটি কিনতে দ্বিধা করে না।
বাংলাদেশে বিনা মূল্যের কোনো সংবাদপত্র আছে বলে আমার জানা নেই। পঁচিশ বছর আগে আমেরিকায় আসার সময় অন্তত আমি এমন কোনো পত্রিকা দেখে আসিনি। নিউইয়র্কে এসে বিনা মূল্যের পত্রিকা দেখলাম। এখানকার দুটি ট্যাবলয়েড আকৃতির ইংরেজি দৈনিক এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক কিছু ইংরেজি পত্রিকা বিনা মূল্যে বিকোতে দেখছি। শুনেছি, কমিউনিটি-ভিত্তিক পত্রিকাগুলো সিটি প্রশাসন বা বিভিন্ন সূত্র থেকে বিজ্ঞাপন বা অন্যভাবে আর্থিক সহায়তা লাভ করে থাকে। আর্থিক সংগতিই তো পত্রিকা প্রকাশনার প্রধান অবলম্বন। যাদের যেমন সহায়তা, তারা সে অনুযায়ী তাদের বিনা মূল্যের পত্রিকার চাকাকে সচল রেখে এগিয়ে যেতে পারছেন।

বিনা মূল্যের পত্রিকার নির্ভরতা পুরোপুরিই বিজ্ঞাপনের ওপর। বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন থেকে আয়Ñএই দুই মিলিয়েই সাধারণত এগিয়ে চলে একটি পত্রিকা। পত্রিকার সার্কুলেশন থেকে পাওয়া আয়কে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। আমি একসময়ের আজাদ, ইত্তেফাক বা সংবাদ-এর কথা জানি, যখন বিজ্ঞাপনের বাজার এত জোরালো ছিল না, তখন সার্কুলেশন থেকে আয়ের ওপরই তাদেরকে বহুলাংশে নির্ভর করতে হতো। কম বিজ্ঞাপন আর বেশি সার্কুলেশন নিয়ে চলা পত্রিকা প্রসঙ্গে আমি গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের গোড়ার দিকের উদাহরণ দিতে চাই। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বিজ্ঞাপনের বাজার ছিল অত্যন্ত সীমিত। দেশে তখন না ছিল তেমন শিল্প-কারখানা, না ছিল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। তাই যতটা বিজ্ঞাপনের আয়, ততটাই নির্ভর করতে হতো সার্কুলেশনের আয়ের ওপর।
এই পরিসরে আমার আলোচ্য বিষয় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলোর প্রচারসংখ্যা। ২০০০ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে আমি যখন নিউইয়র্কে এসে থিতু হই, তখন যতদূর মনে পড়ে, ছয়টি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা এখান থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। ঠিকানা, বাঙালী, বাংলা পত্রিকা, পরিচয়, এখন সময় ও দেশবাংলা। এগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাপ্তাহিক ঠিকানার অবস্থা ছিল রমরমা। সার্কুলেশনে-বিজ্ঞাপনে সবার ওপরে। তাদের পৃষ্ঠাসংখ্যাও ছিল অন্য সবার চেয়ে বেশি। অনেক ধরনের লেখায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি ছিল পাঠকদের প্রথম পছন্দ। বলাই হতো, পত্রিকাটি সর্বাধিক প্রচারিত। আমি তখন আমার এক লেখায় ঠিকানাকে ঢাকার সে সময়ের সর্বাধিক প্রচারিত ইত্তেফাকের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলাম, সাপ্তাহিক ঠিকানা নিউইয়র্কের ইত্তেফাক। অন্য পত্রিকাগুলোর চাহিদাও যে কম ছিল, সে কথা বলা যাবে না। কারণ ঘুরেফিরে সব পত্রিকাই কারও না কারও হাতে দেখা যেত, সব পত্রিকাই ভালোভাবে চলছিল। পাঠকদের রুচির বিষয়টিও তখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পকেটের পয়সা খরচ করে কোনো পাঠককে তার পছন্দের পত্রিকাটি কিনতে দেখে আমি তার রুচিবোধকে বিবেচনায় নিতাম।
তখনকার এই ছয়টি পত্রিকার মধ্যে একটি পত্রিকা ছিল বিনা পয়সার। অন্য পাঁচটি পত্রিকা বিক্রি হতো নির্ধারিত মূল্যে। গুণগত মানে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যায় তারতম্য থাকলেও এই পাঁচটি পত্রিকারই মূল্য ছিল এক ডলার। এক ডলার দিয়ে সবাই পত্রিকা কিনে নিতেন। আর এই বিক্রি থেকেই হিসাব করা যেত কোন পত্রিকার কত কাটতি। বিনা মূল্যের পত্রিকাটি ছিল দেশবাংলা। দেশবাংলা বিক্রি হতো না, অন্য পত্রিকাগুলোর ভিড়ে এই পত্রিকাটি বিনা মূল্যে ‘বিতরণ’ হতো। মূল্য নেই, তাই পত্রিকাটি বিক্রি হতো না, বিতরণ হতো। আর যেহেতু বিনা মূল্যে পাওয়া যেত, তাই মানুষ হাতে হাতে পত্রিকাটি তুলে নিত। এভাবে হাতে হাতে উঠে যাওয়া পত্রিকাটি বলতে হবে ভালোই চলত। ভালো চলত মানে পত্রিকাটিকে তেমন আর রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যেত না। আর যেহেতু রাস্তায় পড়ে থাকত না, সব পত্রিকাই মানুষের হাতে উঠে যেত, তাই পত্রিকাসূত্রে দাবি করা হতো, এটিই সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা।
বিনা মূল্যে পত্রিকা সরবরাহের যে ধারাটি দেশবাংলা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিল, পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট অন্যরা তাকে বাঁকা চোখে দেখলেও ক্রমে ক্রমে এই ধারাটি চালু হয়ে গেল। পয়সা খরচ করে পত্রিকা কেনার বদলে বিনা মূল্যেই যখন পত্রিকা পাওয়া যাচ্ছে, তখন সেটার দিকেই মানুষের দৃষ্টি যেতে লাগল। বিনা মূল্যের পত্রিকার প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখেই সম্ভবত নিউইয়র্কের পত্রিকা-জগতে এক নতুন পরিবর্তন সূচিত হলো। লক্ষ করা গেল, কম চালু পত্রিকাগুলো একটি একটি করে তাদের পত্রিকার মূল্য তুলে দিতে শুরু করল। তারপর চোখের সামনেই দেখলাম, বিনা মূল্যের পত্রিকার একটা জোয়ার সৃষ্টি হলো। সেই জোয়ারে সব পত্রিকাই ভেসে গেল, ক্রমে ক্রমে সব পত্রিকাই বিনা মূল্যের হয়ে গেল।
এমনকি বিনা মূল্যের পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করে যে সম্পাদককে বলতে শুনেছি, মূল্য নেই মানে অমূল্য পত্রিকা, তিনিও তার পত্রিকার মূল্য তুলে দিলেন। ঠিকানার মতো চালু পত্রিকাও তাদের পত্রিকার দাম ধরে রাখতে পারল না, একপর্যায়ে এই জোয়ারের কাছে নতি স্বীকার করল। বাঙালী, বাংলা পত্রিকা, পরিচয়- সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেল। সব বিনা পয়সার পত্রিকায় পরিণত হলো। মনে আছে, দেশবাংলা থেকে তখন উল্লাসভরে বলা হয়েছিল, তারাই বিনা মূল্যে পত্রিকা প্রকাশের পথিকৃৎ।
বিক্রি থেকে আয় নেই, তাই সব পত্রিকারই নির্ভরশীলতা পুরোপুরি বিজ্ঞাপনের ওপর। বিজ্ঞাপনের বাজারও ক্রমে বেশ তেজি হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞাপনের এই তেজি বাজার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর জন্য বেশ সহায়ক ছিল। কিন্তু এই সময়েই উদ্ভব হলো একশ্রেণির সুযোগসন্ধানী কথিত সাংবাদিকের। তারা বিনা মূল্যের সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে পত্রিকা ব্যবসা শুরু করে। তাদের লক্ষ্য সাংবাদিকতা নয়, তাদের লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞাপনের বাজারে থাবা বসানো। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নিউইয়র্কে তখন বাংলা পত্রিকা প্রকাশের একটা হিড়িক পড়ে যায়। ‘ব্যাঙের ছাতা’র মতো গজিয়ে উঠতে শুরু করে নানা নামের তথাকথিত সব পত্রিকা। যেনতেন প্রকারে কয়েক পৃষ্ঠার একটি পত্রিকা বের করে এই মানুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে বিজ্ঞাপনের বাজারে। অভিযোগ শুনেছি, এরা বিজ্ঞাপন আদায়ে ব্যবসায়ীদের ওপর জোর-জবরদস্তি করত। এমনকি বিজ্ঞাপন না দিলে তাদের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লেখারও নাকি হুমকি দিত। একই সঙ্গে পত্রিকা ব্যবসায় একটি ক্ষতিকর কাজ তারা করেছে। তারা বিজ্ঞাপনের বাজারটি নষ্ট করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। বিভিন্ন মাপের বিজ্ঞাপনের জন্য তাদের নির্ধারণ করা রয়েছে বিভিন্ন হার। এই হারের সঙ্গে তারা কোনো আপস কখনো করেনি। কিন্তু বিজ্ঞাপন নিয়ে ওই ‘ব্যাঙের ছাতা’ পত্রিকাগুলোর কোনো নিয়ম-নীতির বালাই ছিল না। যেভাবেই হোক বিজ্ঞাপন আদায় করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তারা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে যা আদায় করতে পেরেছে, তা নিয়েই বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছে। অন্য পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন ছাপতে দিতে হতো ১০০ ডলার, সেই বিজ্ঞাপনই এরা ছেপে দিয়েছে ২৫-৩০ ডলারে। এই অবস্থায় বিজ্ঞাপনদাতারা প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের হার নিয়ে দর-কষাকষির সুযোগ পেয়েছে। দর-কষাকষিতে নির্ধারিত হার থেকে কম মূল্যেই অনেকে বিজ্ঞাপন ছাপতে বাধ্য হয়েছে।
হঠাৎ গজানো পত্রিকায় এই সুযোগসন্ধানী মানুষদের নাম ছাপা হচ্ছিল সম্পাদক হিসেবে। সবাই সাংবাদিকের তকমা লাগিয়ে যেতে শুরু করেছিল নানা অনুষ্ঠানে। সাংবাদিক হিসেবে দখল করে নিচ্ছিল সামনের সারির আসন। একপর্যায়ে হিসাব নিয়েছিলাম, দুই ডজনের মতো পত্রিকা নানা নামে সপ্তাহে সপ্তাহে বাজারে আসছিল। এসব পত্রিকার দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন বিজ্ঞাপনদাতারা। পরে করোনার সময় এসব ‘ব্যাঙের ছাতা’ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। করোনা-পরবর্তীকালে এদের সন্ধান আর পাওয়া যায়নি।
এখন আমরা আবার সেই আদি এবং প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর জগতে ফিরে এসেছি। এসব পত্রিকার প্রকাশকাল কোনোটির সর্বোচ্চ ৩৫ বছর, কোনোটির ৩৪, কোনোটির ২৮ বছর। এত দীর্ঘ বছর ধরে পত্রিকার টানা প্রকাশনা নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে ১৭ থেকে ৭ বছর ধরে। হ্যাঁ, এগুলোকেই আমি বলতে চাই প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা।
প্রতিষ্ঠিত এবং বাজারে চালু এসব পত্রিকা। কিন্তু কোন পত্রিকার প্রচারসংখ্যা কত, তার কোনো হিসাব নেই। না, এ হিসাব পাওয়ারও কোনো উপায় নেই। কারণ সব পত্রিকাই তো বিনা মূল্যের। বিনা মূল্যের সব পত্রিকাই তো মানুষ হাতে হাতে তুলে নিয়ে যায়। কোনো পত্রিকাই পড়ে থাকে না। পড়ে না থাকার অর্থই কি সর্বাধিক প্রচারিত কিংবা বহুল প্রচারিত? এ ক্ষেত্রে সঠিক হিসাব না থাকা সত্ত্বেও দেখছি, বিভিন্ন পত্রিকার মাথার ওপর লিখে দেওয়া হচ্ছে, ‘সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র’, ‘উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত’, ‘Highest Circulated Bangla Weekly In America’ ইত্যাদি সব কথা।
সবাই লিখছেন ‘সর্বাধিক প্রচারিত’। সর্বাধিক মানে তো সবচেয়ে বেশি। এতগুলো পত্রিকা কেমন করে সবই ‘সর্বাধিক প্রচারিত’ হয়? সবিনয়ে জানতে ইচ্ছে করে, কিসের ভিত্তিতে পত্রিকাগুলো সর্বাধিক প্রচারসংখ্যার এমন দাবি করছে? এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি একটি আবেদন জানিয়ে লেখাটা শেষ করতে চাই। পত্রিকাগুলো বিনা মূল্যে বিতরণ না করে আপনাদের ব্যবসার পণ্য হিসেবে একে গণ্য করুন। পত্রিকা বিক্রির ব্যবস্থা করুন। পত্রিকাকে মূল্যহীন না করে, পত্রিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে এর একটা মূল্য ধার্য করুন। পত্রিকার মূল্য পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। মর্যাদা বাড়বে পত্রিকা ব্যবসায়ীদেরও। আর উদয়াস্ত পরিশ্রমের মর্যাদা পাবেন যাদের মেধা আর পরিশ্রমে পত্রিকা পাঠকের হাতে আসে, সেই সাংবাদিকেরা। হোক না পত্রিকার সে মূল্য খুবই সামান্য। হোক না মাত্র একটি কোয়ার্টার, তবু মূল্য ধার্য করুন। এতে পাঠকদের মধ্যেও পত্রিকা কিনে পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে। এ অভ্যাস তো তাদের ইতোপূর্বে ছিলই। আমরাই সেই অভ্যাস নষ্ট করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে আবার গড়ে উঠুক পত্রিকা কিনে পড়ার অভ্যাস। এ অভ্যাস গড়ে ওঠার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের বুঝতে হবে, পত্রিকা বিনা পয়সায় রাস্তায় গড়াগড়ি যাওয়ার বস্তু নয়, পত্রিকা পড়ার বস্তু। পত্রিকা প্রকাশের পেছনে অনেক মেধা কাজ করে। পত্রিকা জ্ঞানচর্চার, বিশ্বকে জানার, বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করার মাধ্যম।
একটি পত্রিকার জন্য একটি কোয়ার্টার ব্যয় করার মতো মানসিকতা পাঠকদের কাছ থেকে আমরা আশা করতেই পারি।
কীভাবে নির্ধারিত হয় পত্রিকার প্রচারসংখ্যা? স্পষ্টতই বলা যায় পত্রিকার বিক্রির হিসাবে। কোন পত্রিকা কত বিক্রি হলো, সেটাই তার সার্কুলেশনের ভিত্তি। হ্যাঁ, বিক্রি। এ কথা তো অনস্বীকার্য, পত্রিকা বিক্রি দিয়েই প্রমাণিত হয় তার প্রচারসংখ্যা এবং প্রচারসংখ্যা দিয়েই বিবেচিত হয় তার জনপ্রিয়তা। যে পত্রিকার যত সার্কুলেশন, সেই পত্রিকাই যে তত জনপ্রিয়, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকার অবকাশ নিশ্চয় নেই। জনপ্রিয়তার যাচাই করেই মানুষ পকেটের পয়সা দিয়ে তার পছন্দের পত্রিকাটি কিনতে দ্বিধা করে না।
বাংলাদেশে বিনা মূল্যের কোনো সংবাদপত্র আছে বলে আমার জানা নেই। পঁচিশ বছর আগে আমেরিকায় আসার সময় অন্তত আমি এমন কোনো পত্রিকা দেখে আসিনি। নিউইয়র্কে এসে বিনা মূল্যের পত্রিকা দেখলাম। এখানকার দুটি ট্যাবলয়েড আকৃতির ইংরেজি দৈনিক এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক কিছু ইংরেজি পত্রিকা বিনা মূল্যে বিকোতে দেখছি। শুনেছি, কমিউনিটি-ভিত্তিক পত্রিকাগুলো সিটি প্রশাসন বা বিভিন্ন সূত্র থেকে বিজ্ঞাপন বা অন্যভাবে আর্থিক সহায়তা লাভ করে থাকে। আর্থিক সংগতিই তো পত্রিকা প্রকাশনার প্রধান অবলম্বন। যাদের যেমন সহায়তা, তারা সে অনুযায়ী তাদের বিনা মূল্যের পত্রিকার চাকাকে সচল রেখে এগিয়ে যেতে পারছেন।

বিনা মূল্যের পত্রিকার নির্ভরতা পুরোপুরিই বিজ্ঞাপনের ওপর। বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন থেকে আয়Ñএই দুই মিলিয়েই সাধারণত এগিয়ে চলে একটি পত্রিকা। পত্রিকার সার্কুলেশন থেকে পাওয়া আয়কে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। আমি একসময়ের আজাদ, ইত্তেফাক বা সংবাদ-এর কথা জানি, যখন বিজ্ঞাপনের বাজার এত জোরালো ছিল না, তখন সার্কুলেশন থেকে আয়ের ওপরই তাদেরকে বহুলাংশে নির্ভর করতে হতো। কম বিজ্ঞাপন আর বেশি সার্কুলেশন নিয়ে চলা পত্রিকা প্রসঙ্গে আমি গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের গোড়ার দিকের উদাহরণ দিতে চাই। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বিজ্ঞাপনের বাজার ছিল অত্যন্ত সীমিত। দেশে তখন না ছিল তেমন শিল্প-কারখানা, না ছিল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। তাই যতটা বিজ্ঞাপনের আয়, ততটাই নির্ভর করতে হতো সার্কুলেশনের আয়ের ওপর।
এই পরিসরে আমার আলোচ্য বিষয় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলোর প্রচারসংখ্যা। ২০০০ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে আমি যখন নিউইয়র্কে এসে থিতু হই, তখন যতদূর মনে পড়ে, ছয়টি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা এখান থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। ঠিকানা, বাঙালী, বাংলা পত্রিকা, পরিচয়, এখন সময় ও দেশবাংলা। এগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাপ্তাহিক ঠিকানার অবস্থা ছিল রমরমা। সার্কুলেশনে-বিজ্ঞাপনে সবার ওপরে। তাদের পৃষ্ঠাসংখ্যাও ছিল অন্য সবার চেয়ে বেশি। অনেক ধরনের লেখায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি ছিল পাঠকদের প্রথম পছন্দ। বলাই হতো, পত্রিকাটি সর্বাধিক প্রচারিত। আমি তখন আমার এক লেখায় ঠিকানাকে ঢাকার সে সময়ের সর্বাধিক প্রচারিত ইত্তেফাকের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলাম, সাপ্তাহিক ঠিকানা নিউইয়র্কের ইত্তেফাক। অন্য পত্রিকাগুলোর চাহিদাও যে কম ছিল, সে কথা বলা যাবে না। কারণ ঘুরেফিরে সব পত্রিকাই কারও না কারও হাতে দেখা যেত, সব পত্রিকাই ভালোভাবে চলছিল। পাঠকদের রুচির বিষয়টিও তখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পকেটের পয়সা খরচ করে কোনো পাঠককে তার পছন্দের পত্রিকাটি কিনতে দেখে আমি তার রুচিবোধকে বিবেচনায় নিতাম।
তখনকার এই ছয়টি পত্রিকার মধ্যে একটি পত্রিকা ছিল বিনা পয়সার। অন্য পাঁচটি পত্রিকা বিক্রি হতো নির্ধারিত মূল্যে। গুণগত মানে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যায় তারতম্য থাকলেও এই পাঁচটি পত্রিকারই মূল্য ছিল এক ডলার। এক ডলার দিয়ে সবাই পত্রিকা কিনে নিতেন। আর এই বিক্রি থেকেই হিসাব করা যেত কোন পত্রিকার কত কাটতি। বিনা মূল্যের পত্রিকাটি ছিল দেশবাংলা। দেশবাংলা বিক্রি হতো না, অন্য পত্রিকাগুলোর ভিড়ে এই পত্রিকাটি বিনা মূল্যে ‘বিতরণ’ হতো। মূল্য নেই, তাই পত্রিকাটি বিক্রি হতো না, বিতরণ হতো। আর যেহেতু বিনা মূল্যে পাওয়া যেত, তাই মানুষ হাতে হাতে পত্রিকাটি তুলে নিত। এভাবে হাতে হাতে উঠে যাওয়া পত্রিকাটি বলতে হবে ভালোই চলত। ভালো চলত মানে পত্রিকাটিকে তেমন আর রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যেত না। আর যেহেতু রাস্তায় পড়ে থাকত না, সব পত্রিকাই মানুষের হাতে উঠে যেত, তাই পত্রিকাসূত্রে দাবি করা হতো, এটিই সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা।
বিনা মূল্যে পত্রিকা সরবরাহের যে ধারাটি দেশবাংলা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিল, পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট অন্যরা তাকে বাঁকা চোখে দেখলেও ক্রমে ক্রমে এই ধারাটি চালু হয়ে গেল। পয়সা খরচ করে পত্রিকা কেনার বদলে বিনা মূল্যেই যখন পত্রিকা পাওয়া যাচ্ছে, তখন সেটার দিকেই মানুষের দৃষ্টি যেতে লাগল। বিনা মূল্যের পত্রিকার প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখেই সম্ভবত নিউইয়র্কের পত্রিকা-জগতে এক নতুন পরিবর্তন সূচিত হলো। লক্ষ করা গেল, কম চালু পত্রিকাগুলো একটি একটি করে তাদের পত্রিকার মূল্য তুলে দিতে শুরু করল। তারপর চোখের সামনেই দেখলাম, বিনা মূল্যের পত্রিকার একটা জোয়ার সৃষ্টি হলো। সেই জোয়ারে সব পত্রিকাই ভেসে গেল, ক্রমে ক্রমে সব পত্রিকাই বিনা মূল্যের হয়ে গেল।
এমনকি বিনা মূল্যের পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করে যে সম্পাদককে বলতে শুনেছি, মূল্য নেই মানে অমূল্য পত্রিকা, তিনিও তার পত্রিকার মূল্য তুলে দিলেন। ঠিকানার মতো চালু পত্রিকাও তাদের পত্রিকার দাম ধরে রাখতে পারল না, একপর্যায়ে এই জোয়ারের কাছে নতি স্বীকার করল। বাঙালী, বাংলা পত্রিকা, পরিচয়- সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেল। সব বিনা পয়সার পত্রিকায় পরিণত হলো। মনে আছে, দেশবাংলা থেকে তখন উল্লাসভরে বলা হয়েছিল, তারাই বিনা মূল্যে পত্রিকা প্রকাশের পথিকৃৎ।
বিক্রি থেকে আয় নেই, তাই সব পত্রিকারই নির্ভরশীলতা পুরোপুরি বিজ্ঞাপনের ওপর। বিজ্ঞাপনের বাজারও ক্রমে বেশ তেজি হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞাপনের এই তেজি বাজার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর জন্য বেশ সহায়ক ছিল। কিন্তু এই সময়েই উদ্ভব হলো একশ্রেণির সুযোগসন্ধানী কথিত সাংবাদিকের। তারা বিনা মূল্যের সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে পত্রিকা ব্যবসা শুরু করে। তাদের লক্ষ্য সাংবাদিকতা নয়, তাদের লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞাপনের বাজারে থাবা বসানো। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নিউইয়র্কে তখন বাংলা পত্রিকা প্রকাশের একটা হিড়িক পড়ে যায়। ‘ব্যাঙের ছাতা’র মতো গজিয়ে উঠতে শুরু করে নানা নামের তথাকথিত সব পত্রিকা। যেনতেন প্রকারে কয়েক পৃষ্ঠার একটি পত্রিকা বের করে এই মানুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে বিজ্ঞাপনের বাজারে। অভিযোগ শুনেছি, এরা বিজ্ঞাপন আদায়ে ব্যবসায়ীদের ওপর জোর-জবরদস্তি করত। এমনকি বিজ্ঞাপন না দিলে তাদের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লেখারও নাকি হুমকি দিত। একই সঙ্গে পত্রিকা ব্যবসায় একটি ক্ষতিকর কাজ তারা করেছে। তারা বিজ্ঞাপনের বাজারটি নষ্ট করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। বিভিন্ন মাপের বিজ্ঞাপনের জন্য তাদের নির্ধারণ করা রয়েছে বিভিন্ন হার। এই হারের সঙ্গে তারা কোনো আপস কখনো করেনি। কিন্তু বিজ্ঞাপন নিয়ে ওই ‘ব্যাঙের ছাতা’ পত্রিকাগুলোর কোনো নিয়ম-নীতির বালাই ছিল না। যেভাবেই হোক বিজ্ঞাপন আদায় করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তারা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে যা আদায় করতে পেরেছে, তা নিয়েই বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছে। অন্য পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন ছাপতে দিতে হতো ১০০ ডলার, সেই বিজ্ঞাপনই এরা ছেপে দিয়েছে ২৫-৩০ ডলারে। এই অবস্থায় বিজ্ঞাপনদাতারা প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের হার নিয়ে দর-কষাকষির সুযোগ পেয়েছে। দর-কষাকষিতে নির্ধারিত হার থেকে কম মূল্যেই অনেকে বিজ্ঞাপন ছাপতে বাধ্য হয়েছে।
হঠাৎ গজানো পত্রিকায় এই সুযোগসন্ধানী মানুষদের নাম ছাপা হচ্ছিল সম্পাদক হিসেবে। সবাই সাংবাদিকের তকমা লাগিয়ে যেতে শুরু করেছিল নানা অনুষ্ঠানে। সাংবাদিক হিসেবে দখল করে নিচ্ছিল সামনের সারির আসন। একপর্যায়ে হিসাব নিয়েছিলাম, দুই ডজনের মতো পত্রিকা নানা নামে সপ্তাহে সপ্তাহে বাজারে আসছিল। এসব পত্রিকার দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন বিজ্ঞাপনদাতারা। পরে করোনার সময় এসব ‘ব্যাঙের ছাতা’ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। করোনা-পরবর্তীকালে এদের সন্ধান আর পাওয়া যায়নি।
এখন আমরা আবার সেই আদি এবং প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর জগতে ফিরে এসেছি। এসব পত্রিকার প্রকাশকাল কোনোটির সর্বোচ্চ ৩৫ বছর, কোনোটির ৩৪, কোনোটির ২৮ বছর। এত দীর্ঘ বছর ধরে পত্রিকার টানা প্রকাশনা নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে ১৭ থেকে ৭ বছর ধরে। হ্যাঁ, এগুলোকেই আমি বলতে চাই প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা।
প্রতিষ্ঠিত এবং বাজারে চালু এসব পত্রিকা। কিন্তু কোন পত্রিকার প্রচারসংখ্যা কত, তার কোনো হিসাব নেই। না, এ হিসাব পাওয়ারও কোনো উপায় নেই। কারণ সব পত্রিকাই তো বিনা মূল্যের। বিনা মূল্যের সব পত্রিকাই তো মানুষ হাতে হাতে তুলে নিয়ে যায়। কোনো পত্রিকাই পড়ে থাকে না। পড়ে না থাকার অর্থই কি সর্বাধিক প্রচারিত কিংবা বহুল প্রচারিত? এ ক্ষেত্রে সঠিক হিসাব না থাকা সত্ত্বেও দেখছি, বিভিন্ন পত্রিকার মাথার ওপর লিখে দেওয়া হচ্ছে, ‘সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র’, ‘উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত’, ‘Highest Circulated Bangla Weekly In America’ ইত্যাদি সব কথা।
সবাই লিখছেন ‘সর্বাধিক প্রচারিত’। সর্বাধিক মানে তো সবচেয়ে বেশি। এতগুলো পত্রিকা কেমন করে সবই ‘সর্বাধিক প্রচারিত’ হয়? সবিনয়ে জানতে ইচ্ছে করে, কিসের ভিত্তিতে পত্রিকাগুলো সর্বাধিক প্রচারসংখ্যার এমন দাবি করছে? এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি একটি আবেদন জানিয়ে লেখাটা শেষ করতে চাই। পত্রিকাগুলো বিনা মূল্যে বিতরণ না করে আপনাদের ব্যবসার পণ্য হিসেবে একে গণ্য করুন। পত্রিকা বিক্রির ব্যবস্থা করুন। পত্রিকাকে মূল্যহীন না করে, পত্রিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে এর একটা মূল্য ধার্য করুন। পত্রিকার মূল্য পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। মর্যাদা বাড়বে পত্রিকা ব্যবসায়ীদেরও। আর উদয়াস্ত পরিশ্রমের মর্যাদা পাবেন যাদের মেধা আর পরিশ্রমে পত্রিকা পাঠকের হাতে আসে, সেই সাংবাদিকেরা। হোক না পত্রিকার সে মূল্য খুবই সামান্য। হোক না মাত্র একটি কোয়ার্টার, তবু মূল্য ধার্য করুন। এতে পাঠকদের মধ্যেও পত্রিকা কিনে পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে। এ অভ্যাস তো তাদের ইতোপূর্বে ছিলই। আমরাই সেই অভ্যাস নষ্ট করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে আবার গড়ে উঠুক পত্রিকা কিনে পড়ার অভ্যাস। এ অভ্যাস গড়ে ওঠার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের বুঝতে হবে, পত্রিকা বিনা পয়সায় রাস্তায় গড়াগড়ি যাওয়ার বস্তু নয়, পত্রিকা পড়ার বস্তু। পত্রিকা প্রকাশের পেছনে অনেক মেধা কাজ করে। পত্রিকা জ্ঞানচর্চার, বিশ্বকে জানার, বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করার মাধ্যম।
একটি পত্রিকার জন্য একটি কোয়ার্টার ব্যয় করার মতো মানসিকতা পাঠকদের কাছ থেকে আমরা আশা করতেই পারি।