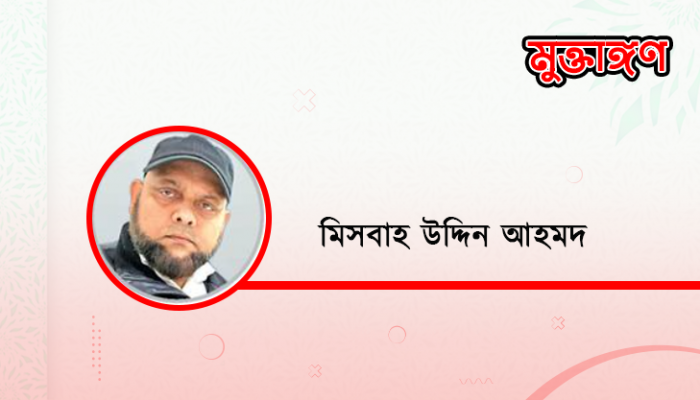কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সব সময় ছিলেন সোচ্চার ও প্রতিবাদী। তার সাহিত্যে সেই সব চেতনার বিস্তর প্রতিফলন রয়েছে। কুসংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ সমাজের কল্যাণ ও মননবিকাশের পথে বড় বাধা হিসেবে মনে করতেন। তাই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার সাহিত্য, প্রবন্ধ, নাটক ও চিঠিপত্রে তিনি এ বিষয়ে সমাজ-সচেতনতা এবং তার ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। কুসংস্কার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :
‘যেখানে যুক্তির অভাব, সেখানেই কুসংস্কারের বাস।’
এ জন্য মানুষকে তিনি মুক্তচিন্তা, যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আধুনিক শিক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সমাজে চেপে থাকা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তি হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। সাহিত্যে ও কুসংস্কারবিরোধী চেতনার প্রসারে তিনি অনেক নাটক ও গল্প লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচিত ‘চণ্ডালিকা’ নাটকের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। যেখানে জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে।
‘প্রমীলা’ নামের চরিত্রটি প্রতিবাদ জানায়, ‘সমাজের অন্য সবার মতো তারও মানুষের মতো বাঁচার অধিকার রয়েছে।’ তেমনি ‘চোখের বালি’ ও ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নারীর অধিকার ও স্বাধীনচেতা ভাবনার মাধ্যমে কুসংস্কারের বিরোধিতাকে প্রবলতর করেছেন। এ ছাড়া ‘সভ্যতার সংকট’, ‘ধর্ম’ প্রভৃতি প্রবন্ধে ধর্মের নামে সমাজে প্রচলিত গোঁড়ামি, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার সাহিত্যযুক্তির ব্যবহার দেখা যায়। তিনি লেখেন :
‘কুসংস্কার কখনো ধর্মের অঙ্গ নয়, বরং তা ধর্মের গলায় ফাঁসির দড়ি।’
সে কারণে শিক্ষাদর্শনে কুসংস্কারবিরোধী মনোভাবের ফলেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞান, শিল্প ও মুক্তচিন্তাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাতপাতের বিভেদের মূলোৎপাটনের প্রত্যাশায় তিনি শিক্ষার কারিকুলাম সাজিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে তিনি বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। একইভাবে বিভিন্ন ভাষাপণ্ডিত শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে :
‘মানুষকে আগে মানুষ হতে হবে-ধর্ম বা জাত নয়, মানবতা প্রধান।’
বাস্তব জীবনে সামাজিক অবক্ষয় ও সাম্প্রদায়িক তার বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, ছুঁত-অছুঁত প্রথার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। একসময় তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করে সমাজে চেপে থাকা ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতা চালান। রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শুধু লেখনীতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বাস্তব জীবনেও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিয়েছিলেন এমন এক সময়ে, যখন হিন্দুসমাজে স্বামী মারা গেলে, স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো! এই অমানবিক বীভৎস প্রথার নাম ছিল ‘সতীদাহ’। কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতীয় সমাজে সতীদাহ প্রথা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম, নিষ্ঠুর বর্বরতার একটি অন্যতম অমানবিক কার্যক্রম। এই ভয়ংকর ও ভ্রান্ত নীতির আলোকে ভারতীয় লোকদের মাঝে সামাজিকভাবে অনেক অমানবিক কুসংস্কারের প্রথা চালু আছে। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার ভারতে যুগ যুগ ধরে চালু ছিল। কট্টরপন্থী ধর্মীয় মৌলবাদী উগ্রবাদ, যা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল।
সতীদাহ প্রথার সেই অনাচারমূলক অন্ধকার যুগে আবির্ভূত হন বিপ্লবী রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায় হিন্দুদের ভয়াবহ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। হিন্দুসমাজের সংস্কারের জন্য তিনি পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গঠন করেন ব্রাহ্ম সমাজ তদুপরি ব্রাহ্ম ধর্ম।
রবীন্দ্রনাথ তাই রামমোহন সম্পর্কে লিখছেন, ‘রামমোহন রায় যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সে এক অতি অগৌরবের অধ্যায়। দেশের চারিদিকে তখন কুসংস্কার, ধ্বংসপ্রবণতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল। যুক্তিহীনতা সত্য ও প্রেমের আলো আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া যাই যে, ভারতের ইতিহাসের এই সর্বাপেক্ষা অবনতির কালে কী করিয়া রাজা রামমোহনের মতো এমন একজন অসাধারণ মানুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল।’ (রামমোহন রায়, ১৭ খণ্ড)
চরম কুসংস্কারপূর্ণ নিকৃষ্টতম ‘সতীদাহ’ প্রথার ভয়ংকর অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ মানসিকভাবে ভীষণ কষ্ট ও পীড়িত ছিলেন। তারও পূর্বে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নিজে এবং ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপকে নিয়ে আন্দোলন করেন। অসাধারণ মেধা ও মননের অধিকারী ডিরোজিও বেঁচেছিলেন মাত্র ২৪ বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি কলেজ শিক্ষকতা থেকে শুরু করে অনেক মানবিক কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৮২৭ সালে তার প্রথম কবিতার বই ‘দ্য পোয়েমস’ প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ সালে প্রকাশিত হয় তার মাস্টারপিস ‘দ্য ফকির অব ঝঙ্গীরা অ্যান্ড আদার পোয়েমস’।
কাহিনিটি এমন যে, ভাগলপুরের নদীতীরের ঝঙ্গীরা নামক আশ্রমে বাস করতেন একজন ফকির। আশ্রমে সেই ফকিরের কার্যকলাপ এবং তার জীবনযাপনের স্টাইল (ধরন) মনোযোগের সঙ্গে খেয়াল করতেন ডিরোজিও। ফকিরের এমন জীবনযাপন ডিরোজিওর কাছে কৌতূহলের জন্ম দেয়। সেই কৌতূহলের কারণেই গল্পের আদলে তিনি লিখে ফেলেন কয়েকটি সেরা কবিতা।
১৪ বছর বয়সে ইংরেজিতে লেখা সেই কবিতাসমূহের মধ্যে ‘ দ্য ফকির অব জঙ্গীরা’ ছিল একটি অন্যতম কবিতা। ২০৫০ শব্দের দীর্ঘ কবিতাটি ১৮২৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটি একটি রোমান্টিক আখ্যান কাব্য, যেখানে জঙ্গীরা (একটি কাল্পনিক স্থান) গ্রামের পটভূমিতে একটি প্রেম ও বিচ্ছেদের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। এই কবিতাটির মাধ্যমে ‘ডিরোজিও’র প্রবল দেশপ্রেম এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে ওঠে। কবিতাটি অবশ্যই ডিরোজিওর সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
গল্পটির মূল চরিত্রে একজন বিধবা নারীকে সতীদাহের বীভৎসতা থেকে উদ্ধার করার স্বরূপটি এমন :
‘একজন সদ্য বিধবা, যাকে স্বামীর সাথে চিতায় পুড়ে মরতে হবে। চিতায় অগ্নিসংযোগ-পূর্ববর্তী সব আচার অনুষ্ঠান শেষে বিধবা নারীটি যখন চিতায় উঠে সূর্যকে প্রণাম করছেন, ঠিক তখন দলবল নিয়ে এক দস্যু এসে ওই নারীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।’
ডিরোজিও কবিতায় প্রবল দেশপ্রেম ও রোমান্টিকতা রয়েছে। যেমন ‘ফকির অব জঙ্গীরা’ কবিতায় :
She was a creature formed to love and bless,
And he was one to love her none the less;
But fate and man had spread their snares between,
And earth was now no more what it had been
‘সেই প্রেম ও ভালোবাসা
ছিল আশীর্বাদের প্রতিমূর্তি,
আর ফকিরও তাকে ভালোবেসেছে
হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে।
কিন্তু
কুসংস্কার সৃষ্টিকারী ফাঁদ পেতে রেখেছিল
নিয়তি আর মানুষের মাঝে,
ফলে, পৃথিবী আর আগের মতো রইল না।’
প্রকাশ থাকে যে, রাজা রামমোহন রায় তখন সতীদাহ প্রথা বিলোপে হিন্দুদের কট্টর পন্থার সঙ্গে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছিলেন। ‘ফকির অব ঝঙ্গীরা’ কবিতা লেখার পরের বছর ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধে আইন করে। গভীর জীবনবোধ ও মানবিকতাসম্পন্ন কবিতাটি ডিরোজিওকে আরও বেশি পরিচিত করে তোলে। ভারতবর্ষের ইংরেজ সাহিত্য সমঝদারগণ ডিরোজিওকে একজন পূর্ণাঙ্গ কবি হিসেবে গণ্য করতে থাকেন।
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সেটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিকতায় পরিণত হয়েছে। তিনি তার রচনার অসংখ্য স্থানে কুসংস্কার ও অমানবিকতার করুণতম গল্পসমূহকে পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। ধর্মের নামে অমানবিকতার তিক্ত বিষয়সমূহকে সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করেন। প্রদীপের আলো সামান্য একটা জায়গাকে আলোকিত করে, প্রদীপের চারপাশের অল্প একটু জায়গা ছাড়া এর কোনো সক্ষমতা নেই। কিন্তু ভোরের আকাশে যখন সূর্য ওঠে, নিখিল ভুবন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে আলো ছড়িয়ে যায় সমস্ত প্রান্তর, পৃথিবীর সমস্ত ভূমির পরতে
পরতে। খণ্ডিত ধর্মের বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।
রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন তিনটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্য দিয়ে সমন্বিত হয়েছে : বেঙ্গল রেনেসাঁ, মধ্যযুগীয় সমন্বয়ী বৈষ্ণববাদ যা অনেকটা সুফিবাদ, আর বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের লৌকিক জীবনধারা। অবশ্য এ বাদে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদও তাকে সাংঘাতিকভাবে আন্দোলিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। এ সময় ভারতবর্ষের মধ্যযুগ পার করে আধুনিক যুগে উত্তরণের বৈপ্লবিক পর্ব।
রবীন্দ্রনাথের মন ছিল আধুনিক, তেমনি তিনি ছিলেন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তিনি মানুষের মননের মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে তার মতের অমিল ছিল। তিনি গান্ধীজির মতো প্রতিনিয়ত প্রার্থনা না করলেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী হয়েই পথ চলতেন। রবীন্দ্রনাথের মতো সে সময় এমন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ জমিদার আর কেউ ছিল না। তিনি বলতেন, তার জমিদারি পরিচালনার সময়টিকে তিনি অজ্ঞাতবাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
সেই অজ্ঞাতবাসের কথা সবার জানা না থাকলেও তার প্রধান অবলম্বন ছিলেন বাংলার মুসলমান চাষিরা। তিনি মুসলমানদের সতীর্থ হিসেবে দেখতেন। হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টানবিরোধী সকল পর্যায়ের মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি বহুবার বলেছেন :
‘আমার ধর্ম বিশ্বজনীতার আকরে সাজানো।’
হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতি তিনি সব সময় গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেকটা ইসলামের সর্বজনীনতার সঙ্গেও তার চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইসলাম সব ধর্মের মানুষকে সম্মান জানিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়েই সহাবস্থানের দীক্ষা দান করে। যদিও কালক্রমে মুসলিমদের একটি বিশাল অংশ সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত থাকতে পারেনি। বর্তমান বিশ্বে তারা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে।
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বজনীন। যদিও সেই বিষয়েও অনেকে একমত নন। ধর্মে অবিশ্বাসী নাস্তিকদের কিছু লোক রবীন্দ্রনাথকে ধর্মবিশ্বাসের মানুষ হিসেবে মানতে নারাজ। কিন্তু এটা সত্যি, রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, একক একটি ধর্ম একটি জাতিকে আলোকিত করে। কিন্তু যে ধর্ম সমস্ত মানবজাতিকে আলোকিত করে, তিনি তার সন্ধান করেছেন। যে ধর্ম পালন করার জন্য অখণ্ড বিশ্ববোধ প্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শিত হয়, তিনি সেই সর্বজনীনতার পক্ষে ছিলেন। তিনি আরও মনে করতেন, অখণ্ড বিশ্ববোধ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মানুষের মধ্যে বিশ্ব সভ্যতার জন্ম দেয়, এ ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বজনীন ধারণার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তিনি ইসলামের নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-কে সকল মানুষের ঊর্ধ্বে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসেবে মনে করেছেন। মহানবীর প্রতি তার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শন অনেক লেখায় প্রকাশ পেয়েছে।
এখানে মানবজাতির অস্তিত্বের সুস্পষ্ট দালিলিক ও বৈজ্ঞানিক দিগ্দর্শন রয়েছে, যা মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনের চূড়ান্ত পথের সন্ধান রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলামের সুস্পষ্ট দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বুঝতে পেরেছিলেন। ইসলামের বিষয়ে খুব জোরালোভাবে বেশি কিছু না লিখলেও প্রকাশ্যে তিনি ইসলামের বিরোধিতা করেননি। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক ও রবীন্দ্র-গবেষক আবু সয়ীদ আইউব বলেন :
‘রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যুক্তির ধর্মে বিশ্বাসী, কোনো সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণকারী নন তিনি।’
এ ছাড়া প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের সর্বজনীন ধারণার ইঙ্গিতও রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মিল পাওয়া যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তেমনি প্লেটোর রাষ্ট্র, সমাজচিন্তার মূলে ছিল শিক্ষার গুরুত্ব ও সাম্যবাদের প্রতি গুরুত্বারোপ। সাম্যবাদ প্রসঙ্গে প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো, যেখানে তিনি শাসক শ্রেণি ও সৈন্যদের জন্য একটি বিশেষ ধরনের সাম্যবাদের প্রস্তাব করেন।
প্লেটোর সাম্যবাদী দর্শনে সম্পত্তিগত সাম্যবাদের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্লেটোর মতে, শাসক ও সৈনিক শ্রেণির কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত নয়। তাদের জন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সাধারণ জীবনযাপন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের বসবাস ও খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। যার মাধ্যমে তারা ব্যক্তিগত লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকবে এবং রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে পারবে।
সামাজিক কুসংস্কারের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে শিক্ষার অভাব ও মূর্খতা। মানুষের মানসিকতা ও মানবিকতার উন্নয়নের জন্য জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ ও প্লেটোর দৃষ্টিতে মূর্খতা একটি মানসিক ব্যাধি ও পাপ। প্লেটো বলেছেন :
‘মূর্খতার চেয়ে বড় পাপ আর নাই।’
‘জ্ঞানীরা কিছু বলার থাকলে কথা বলে আর নির্বোধরা কিছু বলার জন্য বলে।’
প্লেটো আরও বলেন : ‘একটা ভালো সিদ্ধান্ত সর্বদা জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নয়।’
পাপ ও পুণ্যের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক গভীর মানবতাবাদী, আত্মসচেতন ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতেন। তিনি ঐতিহ্যগত ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে গিয়ে এ বিষয়ে এক স্বাধীন ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সেখানে কোনো ধর্মীয় উগ্রতা ও কুসংস্কারের স্থান নেই। এ ক্ষেত্রে কুসংস্কার সমাজের শুধু ব্যাধিই নয়, এটি সামাজিক মহাপাপ।
রবীন্দ্রনাথ পাপ ও পুণ্যকে নিছক কোনো বিধিনিষেধ বা শাস্তিভীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি। বরং তিনি মানুষের আত্মার বিকাশ ও জীবনের সত্যতার সঙ্গে এর সম্পর্ক স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন : ‘পাপ সেই, যা আত্মাকে সংকুচিত করে। পুণ্য সেই, যা আত্মাকে প্রসারিত করে।’
এই দিক থেকে প্লেটোর দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অকাট্য মিল রয়েছে। প্লেটো বলেছেন :
‘পাপী হচ্ছে সেই ব্যক্তিই, যে মানুষের শুধু খারাপ কাজকে প্রকাশ করে আর ভালো কাজ করে গোপন।’
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পাপ ও পুণ্য কোনো বাহ্যিক বিধান নয়, বরং অন্তরের সত্য উপলব্ধি এবং আত্মিক উন্নতির পথের একটি কার্যকরি রূপ।
ধর্মের সরল আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমার গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জ্বালিতে হয় তবে তাহার জন্য আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়Ñসেটুকুর জন্য কত লোকের ওপর আমার নির্ভর। কোথায় সর্ষ বপন হইতেছে, কোথায় তৈল নিষ্কাশন চলিতেছে, কোথায় ক্রয়-বিক্রয়, তাহার পরে দীপ সজ্জারই-বা কত উদ্যোগ—Ñত জটিলতায় যে আলোকটুকু পাওয়া যায় তাহা কত অল্প। তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে। বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না, তাহা কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।’
আবার সমাজের কেউ কেউ মনে করেন, ধর্ম মানেই বিভাজন, কলহ, বিবাদ-বিদ্বেষ, অনৈক্য, তথা দলাদলি। সাধারণের এমন প্রত্যক্ষানুভূতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া, ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।’
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কুসংস্কারের মাধ্যমে মানুষের সকল বিবেকবোধ ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। সেই অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কেও তিনি তার সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।
শিক্ষা খাতে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর ভালোবাসা ছিল।
কুসংস্কারের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ বারবার প্রতিবার মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশ, মুক্তবুদ্ধি, বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানবতাবাদী চিন্তার প্রসারে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।
(রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে লেখাটি রচিত)
লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক।
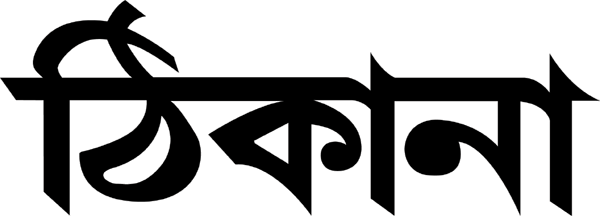
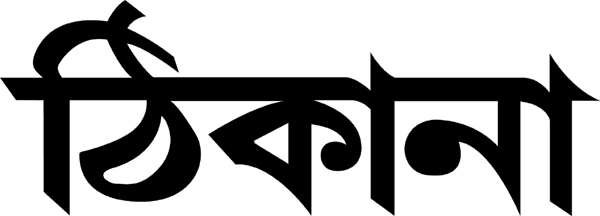

 এবিএম সালেহ উদ্দীন
এবিএম সালেহ উদ্দীন