কিছুদিন আগে একটা খবর পড়ছিলাম। ২০২৩ সালে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় যিনি মিস ইউএসএ নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি তার অর্জনকৃত মুকুটটি ফেরত দিয়েছেন। কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন তার মানসিক অসুস্থতা। তার মতে, এই মুকুট ধরে রাখলে তিনি আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। এর কিছুদিন পরে আরও একজন সুন্দরী, যিনি মিস টিন ইউএসএ হয়েছিলেন, তিনিও তার মুকুট বা টাইটেল ফেরত দিয়েছেন। তাদের দুজনেরই মতে, মানুষের সামগ্রিক সুস্থতার দুটি প্রধান অংশ হলো শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। আর এ দুটির কোনোটার ব্যাপারে কোনো আপস করা উচিত নয়।
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুস্থতা ব্যাপারটা খুবই আপেক্ষিক। আমার কাছে যেটা সঠিক ও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, আপনার কাছে তা পাগলামি মনে হতেই পারে। আবার আমি হয়তো অনেক কিছু হুটহাট করে থাকি, যেটা আমার জন্য নিত্যদিনের বৈচিত্র্য নিয়ে আসে কিন্তু আপনি দেখলে ওটাকে নির্ঘাত পাগলামি মনে করবেন। কে সুস্থ আর কে অসুস্থ, ওই বিচারে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আমাদের জীবন, জগৎ, পরিবেশ ও পরিচিত সার্কেল নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা ক্রমাগত বাধার সম্মুখীন হই, নিজেদের চলার মতো উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করি। আর এই প্রক্রিয়ায় গতানুগতিকের বাইরে আমরা কিছু কাজ করে থাকি, যা কিছু মানুষের চোখে পাগলামি হিসেবে ধরা পড়ে।
মে মাস মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার মাস। এই মাসে আমাদের সবার একবার ভেবে দেখা উচিত, আমরা মানসিকভাবে কতটা সুস্থ। ১৯৪৯ সালে প্রথম মে মাসকে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার মাস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আমেরিকানদের জীবনে মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং কুসংস্কার হটিয়ে মানসিক অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার উদ্্যাপন করতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাসে মানসিক সুস্থতার ব্যাপারে সবাইকে যেমন আলোকিত করা হয়, তেমনি যারা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন, তাদের অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। প্রত্যেক মানুষেরই উচিত নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি ধ্যান দেওয়া-এ কথাটাই এই মাসজুড়ে উপস্থাপন করা হয়। এ ব্যাপারে লোকাল মিডিয়া, বিভিন্ন কর্মসংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ডকুমেন্টারি ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ নানা রকম আয়োজন করে থাকে।
মে মাসজুড়ে দেখা যায় সবুজ রঙের ফিতার আধিক্য। কেউ কেউ সারা মাস জামার ওপর সবুজ ফিতা লাগিয়ে রাখেন এবং এর মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি তার সচেতনতার প্রকাশ ঘটান। মজার ব্যাপার হলো, আঠারো শতকে সবুজ রং সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটা বার্তা প্রকাশ করত, যা দিয়ে বোঝানো হতো মানসিক অসুস্থতা। কিন্তু এই সবুজ রংটিই সময়ের পরিক্রমায় এখন মানসিক সচেতনতার সিম্বল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সবুজ রং এখন নতুন জীবন, সুস্থতা, সম্ভাবনা, সমৃদ্ধি ও অপার শক্তির প্রতীক।
আমেরিকান তরুণ-তরুণীদের জীবনে তাদের বন্ধুবান্ধব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। আমি ক্লাসে বসে আমার ল্যাপটপে এই লেখাটি টাইপ করছিলাম আর পাশের টেবিলে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর আলাপ শুনছিলাম। তারা একটা মেয়েকে নিয়ে কথা বলছিল, যে কিনা ইনস্টাগ্রামে একটা পোস্ট দিয়েছিল। সেই পোস্টের ভিত্তিতে এই মেয়েটাকে ক্যান্সেল করা হয়। অর্থাৎ মেয়েটাকে তার বন্ধুবান্ধবীরা পরিত্যাগ করে। কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না, যোগাযোগ রাখে না বা তার ফোন রিসিভ করে না। সোজা বাংলায় আমরা যাকে সমাজচ্যুত বলি। এ ক্ষেত্রে মেয়েটির সমাজ হচ্ছে তার সহপাঠী বা বন্ধুদের সার্কেল। আমেরিকান স্কুল সিস্টেমে বা টিনএজারদের মধ্যে এই ক্যান্সেল কালচার খুব কমন একটি ব্যাপার। যেসব ছেলেমেয়ে এই ক্যান্সেল কালচারের শিকার হয়, তাদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বা আত্মহত্যার মতো সাংঘাতিক পথ বেছে নেয়।
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসার পাশাপাশি ক্রমাগত গবেষণাও চালিয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে সুইডেন সবচেয়ে এগিয়ে আছে তাদের নাগরিকদের মানসিক রোগের সুচিকিৎসা দিতে। এ ছাড়া জার্মানি, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, জাপান, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর প্রমুখ দেশেও যথেষ্ট ভালো চিকিৎসা ও ব্যবস্থা রয়েছে মানসিক রোগে আক্রান্ত নাগরিকদের জন্য।
মানসিক অসুস্থতার কথা আমরা যেগুলো শুনে থাকি, সেগুলো ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, পিটিএসডি, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, এডিএইচডি, বর্ডার লাইন পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। তবে সবগুলোর মধ্যে ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান মানসিক সমস্যা। যে ৩০০ মিলিয়ন পৃথিবীবাসী ডিপ্রেশনে ভুগছে, তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে বেশি। আমেরিকা ছাড়াও এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ডিপ্রেশনের আধিক্য বেশি। তবে আমেরিকায় যত সহজে মানুষ সাহায্যের জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে যায়, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তত সহজে যায় না।
আমেরিকায় ডিপ্রেশনের কারণ হিসেবে কোভিড-১৯ কে দায়ী করা হয়। এক বছর ধরে ঘরের ভেতর আটকা পড়া নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু সবাই বিভিন্ন রকম নেতিবাচক চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে ক্রমাগত হতাশা ও বিষাদের সাগরে ডুবে যেতে থাকে এবং নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারাতে থাকে। অতিরিক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জীবন থেকে সোশ্যালাইজিংয়ের সময় কমিয়ে দেওয়া, জনসাধারণকে ভীষণভাবে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে এবং নিজের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে ফেলছে।
এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ডিপ্রেশনের একটি বড় কারণ হিসেবে মানা হয়। মানুষের ফেসবুক জীবন ও আসল জীবনের মাঝে আছে আকাশ-পাতাল ফারাক-এই কথাটা আমরা প্রায় সময় ভুলে যাই। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে মানুষ তার হাসি, আনন্দ, বিনোদন ও সফলতার গল্প খুব নিখুঁতভাবে ও গর্বের সঙ্গে পোস্ট করে, যাতে ফেসবুক বন্ধুদের কাছ থেকে লাভ, লাইক ও কমেন্টস পায়। কিন্তু তার মানে কি এই, তাদের জীবনে আর কোনো দুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, হতাশা নেই। আমরা যারা মনের দিক থেকে দুর্বল বা খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী নই, তারা খুব সহজেই অন্য মানুষের সফলতার গল্পের গভীরে তলিয়ে যাই। মনে মনে কষ্ট পাই এই ভেবে যে আমরা কেন ওদের মতো ভাগ্যবান নই, আমাদের জীবনে কেন এত সমস্যা অথচ কিছু মানুষ দিব্যি ভালো আছে। এই চিন্তাই ক্রমাগত আমাদের বিষণ্নতার সাগরে ডুবিয়ে দেয়।
বাঙালি সমাজে শারীরিক অসুখ বা সমস্যা হলে যে কেউ নির্দ্বিধায় বাবা, মা বা স্বামী, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি কোনো মানসিক সমস্যায় ভোগেন, তাহলে তিনি সেটা গোপন করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তরুণ-তরুণী বা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এটা সব সময় দেখা যায়। তার একটি প্রধান কারণ হলো মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের সমাজে কুসংস্কার বা অন্ধ ধারণা বিদ্যমান। অধিকাংশ সময় পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবকে কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে ভেবেই মানুষ পিছিয়ে যায় তার মানসিক সমস্যার কথা কারও সঙ্গে আলাপ করতে। আবার অনেক সময় কেউ হয়তো জানেনই না যে তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন।
এসব ক্ষেত্রে কোনো নির্ভরযোগ্য আত্মীয় বা বিশ্বাসী বন্ধু অবশ্যই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন, যার কাছে ব্যক্তিটি তার মনের কথা খুলে বলতে পারেন। আমাদের দেশে কাউন্সেলিং শব্দটা ইদানীং জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে অসুখী হলে, সন্তানের মধ্যে মানসিক অপরিপক্বতা প্রকাশ পেলে অনেকে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন। তবে বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি পিতা-মাতারও একটি কঠিন দায়িত্ব আছে তাদের ছেলেমেয়েদের ওপর চোখ রাখা, যাতে বিষণ্নতা বা হতাশা খুব প্রাথমিক স্টেজেই ধরতে পারা যায়। বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের প্রতি আরও সময় দেওয়া ও বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথোপকথন করা।
অলস মস্তিষ্ক শয়তানের দোসর। এমন একটা কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রমে এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো মুভমেন্ট। আমাদের মানসিক সুস্থতার জন্য যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। আমরা নিজেদের যতটা সবল ও সক্রিয় রাখব, ততই আমরা মানসিকভাবে শক্তিশালী হব। শারীরিক ফিটনেস বা ব্যায়ামের ওপর ভীষণভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। দৈনন্দিন ব্যায়ামের অভ্যাস মানসিক চাপ ও স্ট্রেস লেভেল কমাতে সাহায্য করে। এমনকি কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় এক জায়গায় বসে না থেকে একটু উঠে গিয়ে করিডোরে হেঁটে আসা বা অল্প সিঁড়ি ভাঙা শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
আমাদের সবারই কমবেশি কিছু পাগলামি স্বভাব আছে। তার মানে এই নয় যে আমরা সবাই পাগল। সাধারণ বাংলা ভাষায় আমরা যেমন বলি, তিনি একটু ছিটগ্রস্ত অথবা তিনি একটু পাগলাটে। তার মানে এই নয় যে তিনি বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে এই ছোটখাটো পাগলামির বাইরেও মনের অসুস্থতা আরও অধিক গভীরে যেতে পারে বা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। মানসিক অসুস্থতা অদৃশ্য কিন্তু খুব ভয়াবহ একটি রোগ, যা তিলে তিলে মানুষের জীবনীশক্তি ও বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা শেষ করে দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে যা কোনো চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে, ওষুধ এবং রুটিন কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সুস্থ থাকা প্রত্যেক মানুষের ন্যায্য অধিকার।
লেখক : ব্লগার ও কলামিস্ট, টেক্সাস।
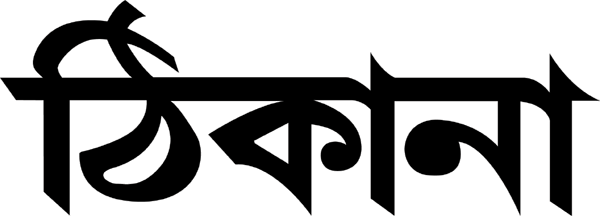
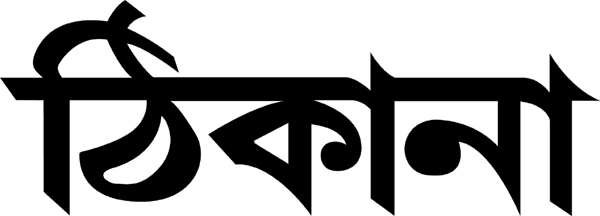



 রোমিনা লোদী জয়িতা
রোমিনা লোদী জয়িতা 








