বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু একজন কবি নন, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রচিন্তক ও সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নদ্রষ্টা। কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের মুক্তির পথপ্রদর্শক এবং গণমানুষের প্রতিনিধি। তাঁর সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে মানুষের কল্যাণকর সেই সব অবদান ফুটে উঠেছে। শিল্পকর্ম, সাহিত্যকর্ম, কাব্যরচনা ও সামগ্রিক জীবনদর্শনে আমরা নজরুলকে দেখতে পাই প্রতিবাদের আইকন, অগ্রসৈনিক ও মহবিপ্লবী হিসেবে, যিনি সকল প্রকার কুসংস্কার, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অন্যায় এবং অসংগতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অপ্রতিরোধ্য এক সাহসী পুরুষ। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ ছিল অসাধারণ। অর্থাৎ শুধু কবি হিসেবে নয়, তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী সমাজসচেতন রাষ্ট্রচিন্তকরূপে সুপরিচিত। বিশেষ করে, কৃষক, শ্রমিক ও নিপীড়িত জনগণের পক্ষে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ও অসামান্য অবদান ছিল। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি ছিলেন সব সময় অগ্রভাগে। শিল্প-সাহিত্যে ছিল তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান।
ব্রিটিশ ভারতের শ্রমিক নির্যাতনের কাহিনি কমবেশি সবারই জানা। সে সময় রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট থেকে যেমন ন্যায্য হিস্সা পাওয়া যেত না, জমিদার ও সমাজের মোড়লদের নিকট থেকেও শ্রমিক তাদের ন্যায্য পাওনা সময়মতো পেতেন না। তখন শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে দাঁড়ানোর মতো সাহসী লোকের সংখ্যা ছিল কম। কৃষক-শ্রমিক ও কুলি-মজুরদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কবিতার ঝংকারে নজরুলই প্রথম আওয়াজ তোলেন। নজরুল তাঁর কবিতায় কৃষক, শ্রমিক ক্ষেত-মজুর এবং সাধারণ মানুষের বঞ্চনার কথা জোরালো ভাষায় তুলে ধরেন। যেমন নজরুল ‘কুলি মজুর’ কবিতায় বলেন :
‘দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সা’ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা’ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ? -চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল্?’
শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব মানবসমাজের একটি প্রাচীনতম সমস্যা। যুগ যুগ ধরে এই সমস্যাটি মানবসমাজকে নানাভাবে আচ্ছন্ন করেছে। মালিকদের নিকট থেকে শ্রমিকদের ওপর চালানো হয়েছে নিপীড়ন ও নির্যাতন। যুগ যুগ ধরে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার্থে বহু আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোনো উদ্যোগ কিংবা ব্যবস্থার তেমন কোনো বাস্তবায়ন ঘটেনি। ফলে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আন্দোলন করতে করতে জীবন কাটাতে হয়েছে অনেককে। ন্যায্য পাওনার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে অনাকাক্সিক্ষতভাবে মেহনতি মানুষের রক্ত ঝরেছে বারবার। এমনকি শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক ‘শ্রম সংস্থা’ (ILO) নামে একটি বিশ্ব সংস্থা পর্যন্ত গঠন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিক-মালিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত হয়নি।
বরং এখনো দেশে-বিদেশে শ্রমিক-মালিক সমস্যা একটি প্রকট সমস্যারূপে বিরাজ করছে। শ্রমজীবী মানুষের রক্তে অহরহ রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। পুরুষের মতো নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও চরম বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিকের নানা সংকট বিরাজমান। বাংলাদেশেও কম-বেশি একই পরিস্থিতি। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সশস্ত্র রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু দুয়েকটা দেশ বাদ দিলে অধিকাংশ দেশেই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথে কালক্ষেপণ করা হয়।
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ছিলেন সোচ্চার। কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের দুর্দশায় তিনি সব সময় ছিলেন চিন্তিত ও পীড়িত। সে জন্যই শ্রমিকদের প্রতি ভালোবাসা ও একাত্মতা প্রকাশ করে তিনি একাধিক কবিতা ও গান লেখেন। মূলত শ্রমিক-মালিক সমস্যাটিকে অধুনা বিবেচনা করা হয়েছে নেহাত একটি শ্রেণিগত সমস্যা হিসেবে। এখানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষই বিষয়টিকে বিবেচনা করছে নেহাত শ্রেণিস্বার্থের দৃষ্টিতে। কিন্তু সমগ্র বিষয়টিকে বিবেচনা করা উচিত মানবিক ও ন্যায়ানুগ দৃষ্টিতে। কত কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রমিক তার আয়-রোজগার করে। কত বড় বড় রাস্তাঘাট, সেতু, দালান-কোঠা, অট্টালিকা এবং প্রাসাদের ওপর রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দেয়। অথচ সেই তুলনায় পারিশ্রমিক পায় নিতান্তই সামান্য। অতএব, শ্রমিক ও মালিক কোনো পক্ষকেই সে বড় কিংবা ছোট করে দেখার সুযোগ নেই; বরং উভয় পক্ষের স্বার্থকে রক্ষা করেই দেখতে হবে পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিতে।
একজন দিনমজুর সারা দিন নিজের শ্রম বিনিয়োগ করেও অনেক সময় মালিকপক্ষের নিকট ন্যায্য মজুরি পায় না, বরং নানা রকম ছলচাতুরীর মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। সেখানে নজরুল ঠিক থাকেন কেমন করে? তিনি প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। তাই তো কবিতাকে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে তিনি লেখেন :
‘হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু’পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!’
‘কুলি-মজুর’ কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের কর্মজীবনের কথা মর্মস্পর্শীরূপে ফুটে উঠেছে। একইভাবে কাজী নজরুল ইসলাম শ্রমজীবী মানুষকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন। এই ‘কুলি-মজুর’ কবিতায় শোষিত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্পষ্ট।
উপমহাদেশে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সূচনাকারী এবং ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামী বন্ধু মুজাফ্্ফর আহমেদের সংস্পর্শে আসার পর নজরুল শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হন। তিনিই মূলত নজরুলকে সাম্যবাদী ও বিপ্লবী রচনা কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেন।
মুজাফ্ফর আহমেদ কলকাতায় ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’ সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকায় কাজ করতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমেদের প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৯১৮ সালে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’য় প্রকাশের জন্য প্রথম লেখা পাঠান কাজী নজরুল ইসলাম। এর পর থেকে দুজনের মধ্যে পত্র লেখালেখি শুরু হয়। মুজাফ্ফর আহমেদ ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯২০ সালে।
একইভাবে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘নবযুগ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যৌথভাবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রাজনীতিবিদ কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ। দৈনিক ‘নবযুগ’ ১৯২০ সালের ১২ জুলাই সান্ধ্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময়ই মুজাফ্ফর আহমেদ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। মুজাফ্্ফর আহমেদের সংস্পর্শে থেকে নজরুল শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনিই মূলত নজরুলকে সাম্যবাদী ও বিপ্লবী কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেন।
শ্রমের দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য সৃষ্টি না করে একই রকম গুরুত্ব প্রদান করে উভয়ের সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবিও তিনি তুলেছেন, যা সে সময় ছিল বেশ আশাব্যঞ্জক এবং প্রগতিশীল ধারণা।
কাজী নজরুল ইসলাম শুধু প্রেম, রোমান্টিক অথবা বিদ্রোহের কবিই নন; তিনি ছিলেন শ্রমজীবী, নিরন্ন ও বঞ্চিত মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর সাহিত্য ও কর্মকাণ্ডে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি, মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং তাঁদের অধিকার আদায়ের স্পষ্ট আহ্বান রয়েছে।
শ্রমজীবী মানুষ ও নিরন্ন মানুষের প্রতি তাঁর ছিল মানবিক টান, সহানুভূতি ও গভীর ভালোবাসা। নজরুল নিজের জীবনে দারিদ্র্য ও অভাবক্লিষ্টতার যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন বলেই শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। নজরুলের কাব্যসমগ্র, সংগীত, নাটক, প্রবন্ধ ও বিশাল রচনাসম্ভার অনাদিকালের জন্য সেই সাক্ষ্য বহন করে আছে। তাঁর মননশীল সাহিত্যকর্মই তাঁকে অমর ও অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। মানুষের সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান চিরস্মরণীয়। ‘দারিদ্র্য’ কবিতায় অসাধারণ শব্দ বুননে নজরুল বলেন :
‘হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কন্টক-মুকুট শোভা।-দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ’ল তরবার!
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস...’
সমাজের দারিদ্র্যের সকরুণ কাহিনিগুলো কতটা বেদনাদায়ক ও কঠিন (!), তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া বোঝানো সম্ভব নয়। নজরুলের অনুভূতিতে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জন্য গভীর মমত্ববোধ ও ভালোবাসা ছিল। তিনি লেখেন :
‘অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি’ সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই-হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি’ কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!’
দারিদ্র্যকে কেবল অভিশাপ হিসেবে না দেখে সাহস ও শক্তিরূপে দেখার পথ খুঁজেছেন। নজরুল তাঁর জীবনের দারিদ্র্যের কশাঘাতকে কীভাবে মোকাবিলা করেছিলেন, তার সেই ক্ষতচিহ্নের কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। তিনিও হয়তো মহামানবের জীবন থেকে দারিদ্র্য মর্মপীড়ন ও শিক্ষা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন। যেমনটি বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনেও ঘটেছিল। মহানবী (সা.) একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহামানবে পরিণত হয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামও হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তাই তো নজরুল চরম দুর্দিনেও ভেঙে পড়েননি। দারিদ্র্য দূরীকরণে হতাশ হননি। বরং দারিদ্র্যকে শক্তি হিসেবে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। নজরুলের কবিতার পরতে পরতে তারই স্বাক্ষর পাওয়া যায় :
‘বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি’ উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম!
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক’রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির সজল
টলটল ধরণীর মত করুণায়!
তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়...’
নজরুল এই বিখ্যাত কবিতায় দারিদ্র্যকে কোনো অভিশাপ বা লজ্জার বিষয় হিসেবে দেখেননি, বরং একে তিনি মহৎ শক্তি ও প্রেরণার উৎস হিসেবে চিত্রিত করেছেন :
‘করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হ’য়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি’
সুন্দরের, কল্যাণের। তরল গরল
কন্ঠে ঢালি’ তুমি বল, ‘অমৃতে কি ফল?
জ্বালা নাই, নেশা নাই. নাই উন্মাদনা,-
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে,
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।’
মোটকথা, দারিদ্র্য কোনো অভিশাপ নয়, বরং মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা এবং নিজের সংগ্রামী জীবনবোধকে জাগ্রত করার এক মহৎ শক্তি। কেননা নজরুলের এই বিখ্যাত কবিতার পঙ্্ক্তিগুলোতে দুঃখী মানুষের কষ্ট-দুর্দশা বর্ণনার পাশাপাশি দারিদ্র্যের প্রতি কবির মনোবেদনার দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এখানে মানুষকেই তিনি মহান মনে করেন কিন্তু দারিদ্র্যকে শত্রু মনে করেন না। বরং সাহসের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন। দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষ না করে জীবনের শক্তি-সাহসিকতার সঙ্গে দারিদ্র্যকে জয় করার কথা বলেছেন। নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নজরুলের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় সমাজের শ্রেণিভেদ দূরীকরণে সহায়ক, যা ধনী-গরিবের সম্পদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেরণা দান করে। নজরুলের কবিতা ও গানে লাখো মানুষের শোষণবিরোধী কণ্ঠস্বর ঝংকৃত হয়েছে। নজরুলের ভাষায়, শ্রমিক-কৃষক, কুলি-মজুরের রক্ত শোষণকারীরা সভ্যতার শত্রু।’
নজরুলের কবিতা শুধু সহানুভূতিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাষ্ট্র ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রেরণা জুগিয়েছে। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অসংখ্য কাব্যধারায় সমাজের নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। সকল মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে নজরুল প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। শ্রমিক ও মালিক ধনী-দরিদ্র কোনো ভেদাভেদ নেই। তেমনি নারী শ্রমিক কিংবা পুরুষ শ্রমিক সকলেরই সমান অধিকার ভোগ করতে হবে। কোনো প্রকার বৈষম্য দেখানো যাবে না। তাই তো নজরুল স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন :
‘আমি সাম্যবাদী!
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।’
কবিতার এই লাইনগুলোতে তিনি শুধু নারী-পুরুষ নয়, বরং সব ধরনের মানবিক সমতার কথা বলেন। সমাজের এই মানবিক মূল্যবোধ নেই বলেই আজ সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বৈষম্য ও অনৈক্য বিরাজ করছে। এখানে নজরুলের শ্রমনীতি ও সাম্যনীতির দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। একইভাবে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকদের ভাষায় তিনি বলেন :
‘আমি চাষা, আমি শ্যামল বর্ণে লাঙল হাতে!’
‘আমি শ্রমিক, আমি মজুর, আমি বেঁচে থাকি কষ্টে!’...
নজরুল তাঁর কালজয়ী কবিতা ও সাহিত্যের শাখায় শাখায় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সমাজের শ্রেণিভেদ ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন।
‘কুলি-মজুর’ এবং ‘দারিদ্র্য’ কবিতা ছাড়াও নজরুল ইসলাম ‘ভিখারী’ কবিতায় ভিক্ষুকের কণ্ঠে ক্ষুধার্ত মানুষের আত্মসম্মান ও বেদনার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনায় দেখা যায়Ñশুধু দান নয়, বরং সমতা ও ন্যায্য বণ্টনই দারিদ্র্য বিমোচনের প্রকৃত পথ প্রশস্ত হবে। ভিক্ষা দিলেই অভাব দূর হবে না। ভিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। সবার জন্য কর্মের সংস্থান এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমেই সমাজের দারিদ্র্য মোচন হবে। একইভাবে সমাজের ভিক্ষাবৃত্তিও উঠে যাবে।
মানুষের স্বাধীনতা, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরে মানবীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পেলেই মানুষ সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পাবে। সমাজের উঁচু-নিচু ভেদাভেদ দূর করে দিয়ে শ্রেণিবৈষম্যের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সকল মানুষের সামাজিক বন্ধন স্থাপন করতে হবে। যার যার প্রাপ্য তার হাতে তুলে দিতে পারলেই দারিদ্র্য দূরীকরণের পথ সুগম হবে।
(লেখাটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত)।
লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক।
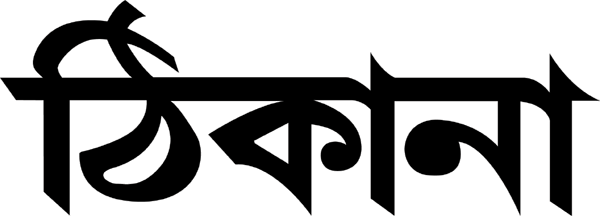
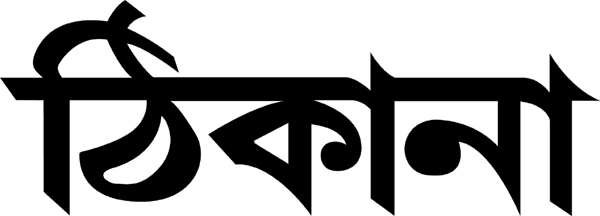

 এবিএম সালেহ উদ্দীন
এবিএম সালেহ উদ্দীন 







