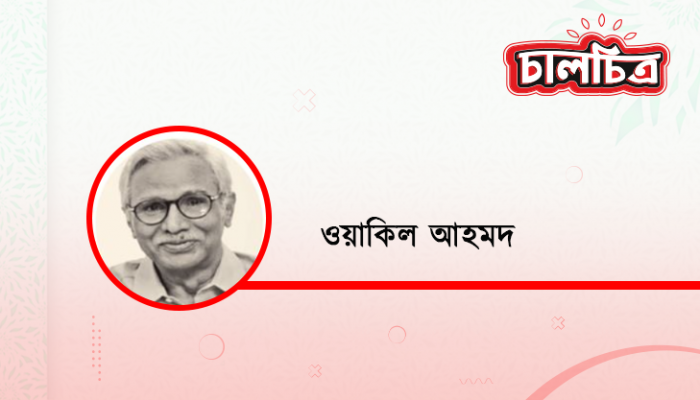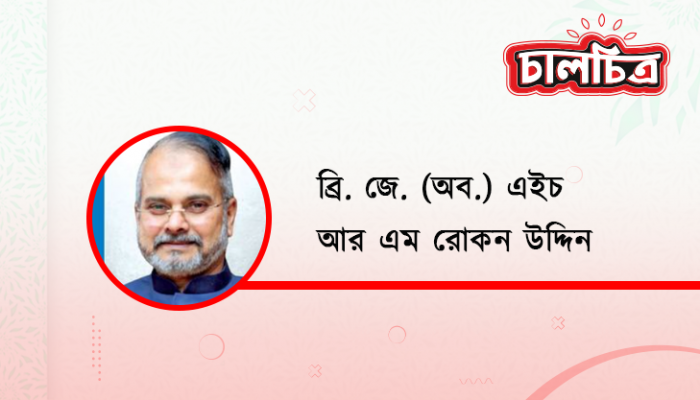শিরোনামটি ফিলিস্তিনের বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ এডওয়ার্ড সাইদের The Responsibility of Intellictual (১৯৯৩) শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদিত ‘মেধাজীবীর দায়’ (২০১৭) থেকে নেওয়া হয়েছে। কলকাতার শিমুল সেন এটি অনুবাদ করেন। গ্রন্থের নাম থেকে বোঝা যায়, এতে সমাজের বুদ্ধিজীবীদের দায়দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে, বুদ্ধিজীবীরা সমাজের বিবেক, তাই সমাজের দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষের পাশে তাঁদের দাঁড়ানো উচিত। তাঁরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন এবং ক্ষমতাবানদের চাটুকারবৃত্তি ত্যাগ করে ক্ষমতার অপব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে সত্য কথা বলবেন।
কবিতা ও ছড়া যেমন সৃজনশীল পদ্যরচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ-স্মৃতিচারণ-সাক্ষাৎকার তেমনি মননশীল গদ্যরচনা। এসব রচনা মসিজীবী লেখকগোষ্ঠীর কাজ। বৃহদার্থে তাঁরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণিভুক্ত। বুদ্ধিজীবীর তালিকায় অন্য যাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, শিল্পীগোষ্ঠী, চিকিৎসক প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে পেশার কারণেই শিক্ষক ও সাংবাদিকদের কাজই হচ্ছে সার্বক্ষণিক লেখাপড়া ও জ্ঞানচর্চা। ‘ইন ট্রু সেন্স’ বা প্রজ্ঞামতে, মেধাবীরাই অগ্রগামী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী।
বিগত আন্দোলনে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কী ছিল? তাঁরা কি বিবেকের যথার্থ পরিচয় দিতে পেরেছেন? দেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ বিক্রি হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে নানা কূটকৌশলে তাঁদের মাথা কিনে নিয়ে সেবাদাসে পরিণত করেছেন। এর একটা কৌশল হলো বৈধ-অবৈধভাবে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশংবদ করা। মনসুর আজিজ একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘যেকোনো আন্দোলনে কবি-লেখকদের একটি বড় ভূমিকা থাকে আন্দোলনকারীদের উজ্জীবিত রাখতে। কিন্তু গত দেড় দশকে বাংলাদেশের কবি-লেখক, শিল্পীসমাজের প্রধান অংশটি ছিল সরকারের উচ্ছিষ্টভোগী। রাজবন্দনা আর সরকারের দক্ষিণা গ্রহণে তাঁরা ছিলেন তৎপর। শুধু মুজিব-বন্দনায় যে পরিমাণ বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তা বিস্ময়কর! রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এটি একটি মচ্ছবে রূপ নেয়। মুজিবকেন্দ্রিক প্রকাশনা মানেই অর্থবিত্তের মালিক বনে যাওয়া।’ (ছোটদের সময়, পৃ. ৬৫) তিনি আরও বলেন, ‘এর বাইরে দেশপ্রেমিক একটি অংশ সরকারি-বেসরকারি প্রচারমাধ্যমে ছিলেন উপেক্ষিত। সে জন্য আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রজ কবি-লেখক-শিল্পীদের এই অংশটি ছিল নীরব। তবে এর বিপরীতে ... একটি ক্ষুদ্র অংশ সরাসরি আন্দোলনে, লেখায় ও সামাজিক মাধ্যমে ছিলেন সরব। প্রবাসী কবি-লেখক-শিল্পীদের ভূমিকাও ছিল চোখে পড়ার মতো।’ (ঐ)
এ প্রসঙ্গে অপর একজন লেখক কাজল রশীদ শাহীনের মন্তব্য স্মরণ করা যায়। তিনি বলেন, ‘... একটা গোষ্ঠী আমাদের লেখক সমাজকে জ্ঞান করতেন ভীতু, সুবিধাবাদী, পদ-পুরস্কার-প্লট-ফ্ল্যাট-বিদেশ ভ্রমণলোভী এক বর্গ বিশেষ। কিন্তু এটা যে গোটা লেখক সমাজের প্রকৃত চিত্র নয়, এর বাইরেও অহংকারের একটা জায়গা রয়েছে, গর্ব ও গৌরব করার মতো পরিসর ও কীর্তি আছে, তা জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে।’ (গণঅভ্যুত্থানে আহত কবি ও লেখক, কালের ধ্বনির বিশেষ প্রকাশনা, পৃ. ২৫)
দ্বিতীয় উক্তির প্রথমাংশ নিয়ে আমাদের অনেক কিছু বলার আছে। বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-পদ-প্রতিষ্ঠা পাওয়ার দরকার আছে। বিশেষ করে, কবি-লেখক-শিল্পীরা লেখেন, চিত্র আঁকেন নিজের অন্তর তাগিদে সত্য, তবে জাতির ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেলে তাঁরা উৎসাহ পান, অনুপ্রাণিত হন। আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে সুকৌশলে তাঁদের মেধা কিনে নিয়েছিল। ‘পদ-পুরস্কার-প্লট-ফ্ল্যাট-বিদেশ ভ্রমণলোভী’ কবি-লেখক-শিল্পীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক-সাংবাদিকরাও বাদ যান না। তাঁদের মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন সত্তা হরণ করা হয়। তাঁরা সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ‘ছয়কে নয়, নয়কে ছয়’ বানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আওয়ামী লীগের একক সম্পদে পরিণত করেন, শেখ মুজিবের দেবত্বকরণ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। প্রবাসী গবেষক ড. সাইমুম পারভেজ বলেন, “মুজিবের ‘দেবতাসুলভ’ বৈশিষ্ট্যকে সামনে নিয়ে আসতে ৭ মার্চে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ ও ‘মুজিব ছাড়া দেশ স্বাধীন হতো না’Ñএ বয়ান সামনে নিয়ে আসা হয়। ... মুজিবকে ‘একক নেতা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর বক্তৃতা, তর্জনী, চশমা, কোট ও পাইপকে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রতীকী উপস্থাপন শুরু হয়। বিশেষ করে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পরিসরে শেখ মুজিবের সর্বময় উপস্থিতিÑটাকার নোট, বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড, সংবাদপত্র, পাঠ্যবই, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ও নেতাদের বক্তৃতায় প্রতিদিন বারবার উল্লেখ করে মুজিবকে একটি ‘অদৃশ্য শক্তি’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই সর্ববিরাজমানতা একটি দৃশ্যমান কিন্তু দেবত্বকরণ তৈরি করে, ... মুজিবকে বটবৃক্ষের মতো মহিরুহ করে।” (প্রথম আলো, ২১-৮-২৫)
শেখ হাসিনার শাসনামলে শিক্ষা-সংস্কৃতি-গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ করা হয়। এ কাজে বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিস্বার্থে সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেন। প্রায় ৮০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, প্রভোস্ট ইত্যাদি প্রশাসনিক উচ্চ পদগুলোতে নিয়োগ পেয়ে কারা অধিষ্ঠিত ছিলেন? প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউজিসি ও জাতীয় অধ্যাপকের মতো প্রেস্টিজিয়াস একাডেমিক পদগুলোতে কারা নিয়োগ পেয়েছেন? ১৫ বছরের রেকর্ড দেখলেই সব ঝরঝরে হয়ে যায়। নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার পরিবর্তে দলীয় সমর্থকদের প্রাধান্য দেওয়া হতো। মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরির প্রত্যাশায় শিক্ষার্থীদের যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তার ৫৫% যেত কোটার কবলে, বাকি ৪৫% পদও মেধাবীরা পেতেন না, নিয়োগ পেতেন দলীয় বিবেচনায় ক্যাডাররা। লিস্ট যেত দলের হাইকমান্ডের কাছ থেকে। সে খবরও আমরা শুনেছি। অর্থাৎ মেধাবীদের ভাগ-ভোগের খাতা শূন্য। এসব কথার কথা বা বানোয়াট নয়, অতি বাস্তব সত্য এবং শতভাগ সত্য।
আরও কতক দৃষ্টান্ত দিই। এই সময়ে বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন (সোনারগাঁও) ইত্যাদি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ডিজি-পরিচালক পদে কে বা কারা কর্মরত ছিলেন? এমনকি এসব প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ড ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যরাও বাদ যান না। রেজিম চেঞ্জ হলে ‘খোলনলচে’ও বদল হতো। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি : ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। আমি বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলাম। মেয়াদ শেষ না হলেও নতুন করে গঠিত হলো ট্রাস্টি বোর্ড। ওবায়দুল কাদের হলেন চেয়ারম্যান। বোর্ডের প্রথম সভাটি ছিল নতুন-পুরাতন সদস্যের মিলিত বৈঠক। চেয়ারম্যান নতুনদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, ‘তোমরা খুশি হয়েছ তো!’ নতুনদের মধ্যে একজন ছিল আমার ছাত্রীÑকবি বেবী মওদুদ। রাজনীতিতে শিক্ষক কুপোকাত!
২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংখ্যা কয়েকশ হবে। তাঁরা মতাদর্শের দিক থেকে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক, একটু খোঁজ নিলে ‘থলির বিড়াল’ বেরিয়ে আসবে। আওয়ামীপন্থী ছাড়া বিরোধী মতের একজনেরও নাম পাওয়া যাবে না। মেধার বিচার কোথায়? দলীয়করণ চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির বয়ান তুলে জাতির মধ্যে বিভক্তিকরণও বাড়ছিল।
ভিন্নমতের বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের জন্য তৈরি হয়েছিল ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন’। শেখ মুজিব, শেখ হাসিনা বা সরকারের কোনোরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করা যাবে না, করলে গ্রেপ্তার, মামলা, জেল, জরিমানার মতো শাস্তিভোগ নির্ধারিত ছিল। এর উপরেও ছিল গুম-খুনের মতো মৃত্যু-পরোয়ানা। ফরহাদ মাযহারের মতো একজন স্পষ্টবাদী প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব ঢাকা থেকে একদিন নিখোঁজ হয়ে গেলেন। দিন কতক ‘নাই’ থেকে তাঁকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি জায়গায় পাওয়া গেল। রাজনীতিবিদ বিএনপির প্রথম সারির নেতা সালাহউদ্দিন আহমদের ঘটনা সবাই জানেন। বছরের পর বছর ধরে তাঁকে কত নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছে! গুপ্ত টর্চারসেল ‘আয়নাঘরে’র রহস্য পরে জানা গেছে। সেখানে কত কী ঘটেছে, তার আংশিক জানা গেছে, বাকিটা অজানা রয়ে গেছে। মোটকথা, আওয়ামী সরকার সারা দেশে একটা ‘ভয়ের সংস্কৃতি’ তৈরি করেছিল। নতুন প্রজন্মের তরুণেরা তো বলেই ফেললেন, ‘উই হেট পলিটিকস’Ñআমরা রাজনীতি ঘৃণা করি! প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ বছর গদিতে থেকে এসব কেন করেছেন? তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ববাদ ও একচ্ছত্র আধিপত্য অটুট রাখতে যা যা করা দরকার, ন্যায়নীতি বিবেক মনুষ্যত্বের মাথা খেয়ে তা-ই করেছেন, দ্বিধা করেননি। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যখন নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলছে, তখন ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, শিক্ষক-লেখক-শিল্পী শেখ হাসিনার কার্যালয়ে হাজির হয়ে তাঁকে মদদ জুগিয়েছেন। তাঁরা এটা করেছেন লোভ বা রিপুর বশে। রিপুর কাছে বিবেক পরাজিত হয়েছে।
এখন ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই। বদরুদ্দিন ওমর, সিরাজুল ইসলাম চৈধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হকের মতো বুদ্ধিজীবী মাঝে মাঝে কিছু লেখালেখি প্রকাশ করতেন, তাঁরা ক্রমশ নীরব হয়ে যান। ঘাড়ে মাথা তো একটাই! বস্তুত শেষের দিকে একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা। দেশের এমনই এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে এল শিক্ষার্থীদের কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সেটা দেখতে দেখতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে পরিণত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষক একক অথবা দলগতভাবে আন্দোলনরত ছাত্রদের সমাবেশে হাজির হয়ে বক্তব্য দেন। ৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী সাদা দলের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে একটি বিবৃতি দেন। দলের পক্ষে এতে স্বাক্ষর করেন আহ্বায়ক মো. লুৎফর রহমান খান (বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য), যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও অধ্যাপক আবদুস সালাম। (প্রথম আলো, ৬-৭-২৪)
১৬ জুলাই ‘রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কাছে শিক্ষকরা অসহায়’ শিরোনামে ‘প্রথম আলো’ পত্রিকায় মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, ‘কোটা নিয়ে সমস্যাটি একেবারেই মীমাংসিত সমস্যা। এখন যে সমস্যাটি তৈরি হয়েছে, সেটি সমাধানে সরকারের কাছ থেকে একটা যৌক্তিক আশ্বাস লাগবে। রাগ, ক্ষোভ, জেদাজেদি নয়; একটা যৌক্তিক ও সহনীয় সমাধান প্রত্যাশা করি।’ ( ১৭-৭-২৪) একদিন সাদা দলের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের প্রতিবাদে কলাভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করেন।
১০ জুলাই ঢাবির আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল (বর্তমানে আইন উপদেষ্টা) শিক্ষার্থীদের সমাবেশে বক্তৃতা, বিভিন্ন বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান এবং পত্রিকায় নিবন্ধ রচনার মাধ্যমে তাঁদের সমর্থনে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বেশ সক্রিয় ছিলেন। ‘কোটা বিতর্ক : সমাধান সরকারের হাতে’ শীর্ষক উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি আইনের দিক থেকে কোটাপ্রথার স্বরূপ তুলে ধরে বলেন, ‘গণপরিষদে বিতর্ককালে কোনো অনুচ্ছেদে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি চাকরিতে কোটা দেওয়ার কথা বলা হয়নি, তবে ১৫ অনুচ্ছেদের আলোচনাকালে পঙ্গু ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের কথা আলোচিত হয়েছে। সে আলোকে তাঁদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ও অন্যান্য ভাতা প্রদান সংবিধানসম্মত। কিন্তু ঢালাওভাবে সব মুক্তিযোদ্ধাকে সরকারি চাকরিতে অনাদিকাল ধরে কোটা প্রদান সংবিধানসম্মত নয়।’ (প্রথম আলো, ১১-৭-২৪)
১৯ জুলাই শাহবাগে অভিভাবকদের এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, ‘আপনারা সংলাপের কথা বলেন, আবার একই দিনে মানুষ হত্যার নির্দেশ দেন। এটা এখন কোটা সংস্কারের আন্দোলন নয়, রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলন। আমরা আমাদের সন্তানদের পাশে দাঁড়িয়েছি।’ (প্রথম আলো, ২০-৭-২৪) ১ আগস্ট ‘বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ’ আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের সব শিক্ষার্থীকে যদি ছেড়ে দেওয়া না হয়, যদি হত্যার বিচার করা না হয়, তাহলে বিক্ষুব্ধ নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে আরও কঠোর ও অব্যাহত কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে, ছয় সমন্বয়ককে তুলে আনার ঘটনায় ডিবিপ্রধান হারুনের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা হওয়া উচিত।’
‘বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক’ (২০১৪) নামক বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্ল্যাটফর্মের অধীনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সমর্থনে শিক্ষকদের সমাবেশ, মানববন্ধন, বিবৃতির মাধ্যমে একাধিক কর্মসূচি পালন করতে দেখা যায়। ‘শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে হত্যাকাণ্ড, হামলা ও নির্যাতনের সাথে জড়িতদের শাস্তি দিতে হবে’ শিরোনামে শিক্ষকগণ ১৬ জুলাই এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘কোটা সংস্কারের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার্থী আন্দোলনের ওপর গুলি চালিয়ে রক্তাক্ত করা হলো বাংলাদেশকে। মিডিয়ার বরাতে জানা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন জেলায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে ৫ জন শিক্ষার্থী আন্দোলনকারী। দেশব্যাপী আহত হয়েছেন হাজারখানেক শিক্ষার্থী। গত ১৫ জুলাই দিনভর ও ১৬ জুলাই প্রথম প্রহরে ছাত্রলীগ নামধারী গুন্ডা ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নামিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর নারকীয়, ভয়াবহ ও মর্মান্তিক হামলা চালানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে। ...এসব ন্যক্কারজনক হামলার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসনকে যেভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে, তা আমাদেরকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আমরা গভীর উদ্বেগ ও বেদনার সঙ্গে এসব হত্যাকাণ্ড ও হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। একই সঙ্গে এসব হত্যাকাণ্ড ও হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।’ এতে ৮৫ জন শিক্ষক অনলাইন স্বাক্ষর করেন। (ইন্টারনেট, দ্র. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক)।
‘জুলাই হত্যাকাণ্ড, গণগ্রেপ্তার এবং নির্যাতনের প্রতিবাদে/ নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশ/ সকাল ১০-৩০টা ২৯শে জুলাই শুরু শাহবাগ, শেষ অপরাজেয় বাংলা’ তিন সারিতে লেখা ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকগণ এরূপ একটি কর্মসূচি পালন করেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস। শিক্ষার্থীসহ দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনাকে ‘জুলাই হত্যাকাণ্ড’ নামে অভিহিত করে সভাপতি বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের প্রতিপক্ষ ভাবা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের খোলনালচে পাল্টে দিতে এসেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রে যে নৈরাজ্য চলেছে, হলগুলোয় ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের যে সুপরিকল্পিত নিপীড়ন চলেছে, সেই সবকিছু পাল্টে নতুন ইতিহাস লেখার পথ তৈরি করেছেন এই শিক্ষার্থীরা।’ সমাবেশে আর যাঁরা বক্তৃতা দেন, তাঁরা হলেন ঢাবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন, বুয়েটের অধ্যাপক আবদুল হাসিব চৌধুরী, জবির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক নাসিরউদ্দিন আহমদ। অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রুশাদ ফরিদী, খুবির শিক্ষক আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী, ব্র্যাক বিশ্ববিদালয়ের সাইমুম রেজা তালুকদার প্রমুখ।
তাঁরা ১ আগস্ট ‘নিপীড়নবিরোধী সমাবেশ’ ব্যানারে ‘অপরাজেয় বাংলা’র (ত্রিমূর্তি) পাদদেশে সমবেত হয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। ঢাবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান বলেন, “প্রতিবাদ করলে ‘ট্যাগ’ (তকমা) লাগানো হয়। এটা বন্ধ করতে হবে। এই প্রজন্মকে ট্যাগ দিয়ে থামিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রতিটি হত্যার বিচার করতে বাধ্য করতে হবে।” আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, ‘সরকারের পদত্যাগের দাবি উঠেছে। খুনের বিচার না করতে পারলে, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে না পারলে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। খুনের বিচার অন্য খাতে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, বলা হচ্ছে-সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারা গেছে। শিক্ষার্থীদের অনিরাপদে রেখে শিক্ষকেরা শান্তিতে ঘরে বসে থাকবেন না।’ পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম বলেন, ‘আজকে পুলিশ আমার শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরেছে, তাকে কথা বলতে দিচ্ছে না। এই বাংলাদেশ কি আমরা দেখতে চেয়েছি?’
বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা শিক্ষকদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ৩৬ দিনের আন্দোলনের দিনগুলোতে প্রিন্ট মিডিয়ায় যাঁরা প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ফিচার লিখেছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা জানা যাবে সমকালের পত্রপত্রিকা থেকে। আমি দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রভৃতি কতক পত্রিকার সবগুলো সংখ্যা থেকে তথ্য নিয়ে যাঁদের রচনার সন্ধান পেয়েছি, মৎপ্রণীত ‘জুলাই-আগস্ট ’২৪ গণঅভ্যুত্থান : ইতিহাস ও অন্যান্য’ (২০২৫) গ্রন্থে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। লেখকগণ চলমান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সরকারের গৃহীত নীতির সমালোচনা করেছেন ও সব রকম অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার চেয়েছেন। উল্লেখ থাকে যে, কয়েকজন সরকার সমর্থক শিক্ষক এবং কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমের মতো রাজনীতিবিদ প্রবন্ধ লিখে বর্তমান বিরাজমান অপ্রকৃতস্থ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এবং সরকারকে সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করার পরামর্শ দিয়েছেন।
এভাবে সুজন, সিপিডি, বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ, উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, সন্তানের পাশে অভিভাবক ইত্যাদি সংগঠনের নেতাকর্মীদের আন্দোলনে সমর্থনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংযোগ, সংহতি ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ গণনায় নিলে বুদ্ধিজীবীদের অ্যাক্টিভিটির পরিমাণ জানা যায়। তাঁরা অবস্থার বিপাকে একসময় নীরব ছিলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলন তাঁদের মুক্তি দিয়েছে, তাঁরা সাহস পেয়েছেন তাঁদের নির্ভীক ভূমিকা ও বীর শহীদদের আত্মবলিদান থেকে, তাঁরা ভয়-দ্বিধা-শঙ্কা ঝেড়ে ফেলে সরব ও সক্রিয় হয়ে রাজপথে নেমে এসেছেন। সুতরাং সব বুদ্ধিজীবীর বিবেক মরে যায়নি, সাময়িক চাপা পড়েছিল মাত্র। আমাদের শেষ কথা-আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা সকলের সহযোগিতায় যা করার, তা সম্পন্ন করেছেন। এখন যা বাকি আছে-যে উদ্দেশ্যে এত ত্যাগ স্বীকার, রক্তপাত, প্রাণহানি, স্বজনদের আহাজারি, তার প্রতিকার ও নিরাময় করা। স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে। এখন দরকার-দুঃশাসন, দুর্নীতি নির্মূল করে রাষ্ট্র ও সমাজকে মুক্ত করা। যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তার অবসান ঘটিয়ে সাম্য, ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা জনবান্ধব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এসব কাজ কে করবে? নিঃসন্দেহে তা শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক হিসেবে সব দায়দায়িত্ব সুশীল ও মেধাজীবী তথা বুদ্ধিজীবীদের ওপর বর্তায়। শিক্ষার্থীদের অনেকের শিক্ষাজীবন শেষ হয়নি; তাঁরা তরুণ, অভিজ্ঞতার অভাব আছে তাঁদের। অপরদিকে জনতা কোনো সংগঠিত শক্তি নয়, তাঁদের ধ্যান-ধারণা মিশ্র ও অনধিগম্য। মেধাজীবীদের স্বপ্ন আছে, চিন্তাশক্তি আছে, সৃজনশীল প্রতিভা আছে, ভিশন মিশন ইমাজিনেশন আছে। সুতরাং দায়িত্ব তাঁদেরই নিতে হবে। এখন তাঁদের কাজ হলো-জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাক্সক্ষাকে ভাষা দেওয়া, চেতনা ও প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অংশ করে প্রতিদিনের চর্চায় তার সজীবতা প্রবহমানতা বজায় রাখা, যত দিন না লক্ষ্য অর্জিত হয়। [চলবে]
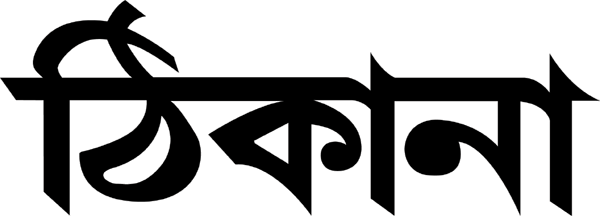
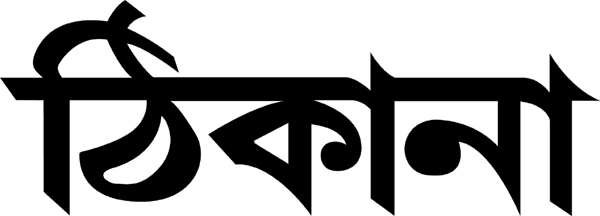

 ওয়াকিল আহমদ
ওয়াকিল আহমদ